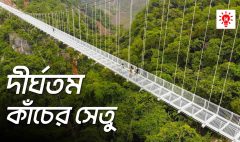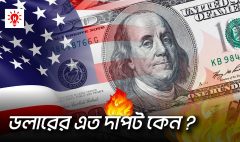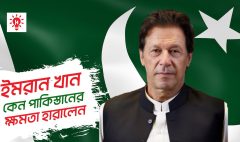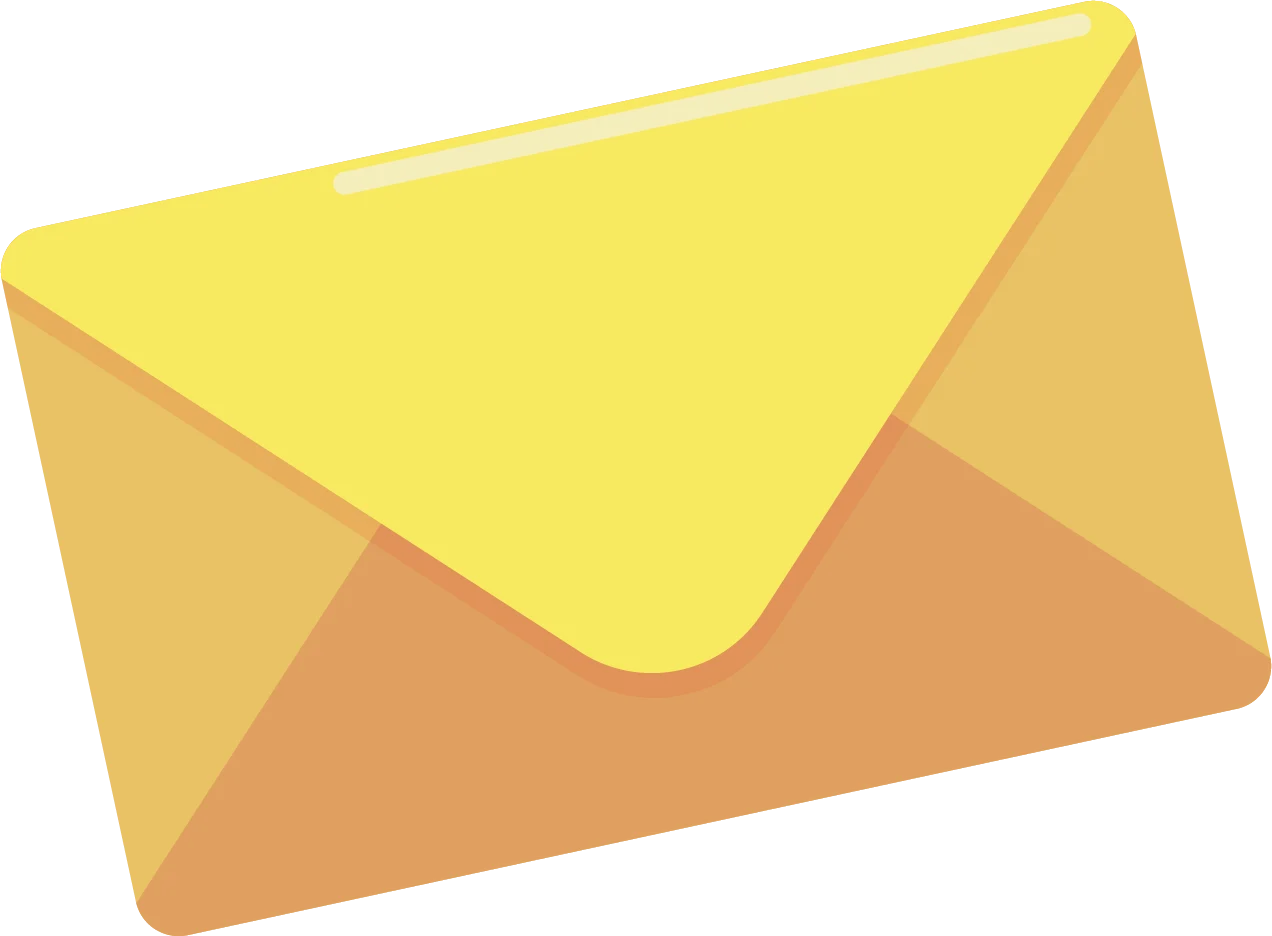সরকার কেন আইএমএফের ঋণ নিচ্ছে
সরকার কেন আইএমএফের ঋণ নিচ্ছে
বাংলাদেশ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ এর কাছে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার বা ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা চেয়েছে। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে, বাংলাদেশের রিজার্ভ চাঙা করতে এবং মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীল আনতে এই অর্থ কাজে লাগানো হবে। যদিও মাত্র কয়েক মাস আগেও বাংলাদেশ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রতবর্ধশীল অর্থনীতির দেশ। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকেও বারবার দাবি করা হচ্ছিল যে, বাংলাদেশের রিজার্ভ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তারপরও হঠাৎ কেন সরকার এত বিপুল অর্থ ঋণ নিতে হচ্ছে তা অনেকের মনেই প্রশ্ন। সম্প্রতি দেশের বাজারে জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পেছনেও, আইএমএফ এর ঋণ চুক্তিকে দায়ী করা হচ্ছে। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠা হিসেবে বিশ্বব্যাপী আইএমএফের কুখ্যাতি আছে। অতীতে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং আফ্রিকার বহু দেশের অর্থনীতি আইএমএফের ঋণ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বাংলাদেশ কেন আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নি”েছ তা ভালোভাবে বুঝতে হলে, দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। একটি বিষয় হল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং আরেকটি বিষয় হল ব্যালেন্স অব পেমেন্ট। প্রথমেই আসা যাক রিজার্ভের বিষয়ে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশও মার্কিন ডলার কে রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার করে। তাই বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি, রেমিট্যান্স, ঋণ বা অ্যন্যান্য উৎস থেকে সরকার যে ডলার আয় করে; তা দিয়ে দেশের আমদানি ব্যয় এবং ঋণ ও সুদ সহ যাবতীয় খরচ মেটানোর পর; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যে পরিমাণ ডলার সঞ্চিত থাকে, সেটাই মূলত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এরপর আসা যাক ব্যালেন্স অব পেমেন্টের বিষয়ে। যেকোন দেশের অর্থনীতির জন্য ব্যালেন্স অব পেমেন্ট বা লেদেনের ভারসাম্য খুবই গুরুত্বর্পূর্ণ। সাধারনত আমদানি রাপ্তানির আর্থিক হিসেবকেই ব্যালেন্স অব পেমেন্ট বলা হয়। ব্যালেন্স অব পেমেন্ট কে প্রাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১. কারেন্ট একাউন্ট এবং ২. ক্যাপিটাল একাউন্ট। কোন দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য, জ্বালানী, গাড়ি, স্বর্ণ সহ যাবতীয় আমদানি রপ্তানির হিসেব থাকে কারেন্ট একাউন্টে। অন্যদিকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিনিয়োগ, ঋণ এবং ব্যাংকিং তথ্য ক্যাপিটাল একাউন্টে হিসেব করা হয়। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রিজার্ভ এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্টে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দি”েছ। সাধারণত দেশ থেকে পন্য রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়, সেই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়েই আবার প্রয়োজনীয় পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। কিš‘ ডলারের বিপরীতে টাকার মান অনেক কমে যাওয়ার কারণে, পণ্য আমদানি করতে বাংলাদেশের রিজার্ভ থেকে প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছিল। সেই সাথে বাংলাদেশের বাজেটেও ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার একটি বিশাল অঙ্কের ঘাতটি আছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে, বৈদেশিক লেনদেন পরিমিতির উন্নতি ঘটাতে, বাংলাদেশের রিজার্ভ চাঙা করতে এবং মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতেই মূলত, সরকার আইএমএফের কাছে ঋণ চেয়েছে। এর আগেও কয়েকবার আইএমএফ থেকে ঋণ সহায়তা নিয়েছে বাংলাদেশ, কিন্তু কোনো বারই ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলারের বেশি ছিল না।
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত বছর ছিল ৪৫.৫ বিলিয়ন ডলার। কিš‘ জুলাই মাসের শেষ নাগাদ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৭.৬৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ রিজার্ভ আছে, তা দিয়ে ছয় মাসের বেশি প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির মূল্য পরিশোধ করা যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাস, খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি, বাংলাদেশের আমদানিও অনেক বেড়েছে। ফলে দেশীয় বাজারে ডলারের চরম সংকট তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার সরবরাহ বাড়িয়ে পরি¯ি’তি ¯ি’তিশীল করার চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা কাজে আসছে না। সরকার বলেছে, গত বছরের তুলনায় এই বছর আমদানি বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ফলে ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের কারেন্ট একাউন্টে ১৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। গত দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থীতিতে এ ধরনের সঙ্কট তৈরী হয়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার বুঝতে পেরেছে যে, অন্য জায়গা থেকে ডলার সরবরাহ বাড়িয়ে এই ঘাটতি প‚রণ করা সম্ভব নয়। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই আইএমএফের দ্বার¯’ হয়েছে বাংলাদেশ। ‘বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ায় সবসময়ই কিছুটা ঘাটতি থাকে। কিš‘ সেই ঘাটতি যদি অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পরি¯ি’তি মোকাবেলা করা হয়।
আইএমএফ কোন দেশ কে ঋণ দিলে, সেই সাথে দেশের নীতগত কিছু বিষয় সংস্কারের শর্তও জুড়ে দেয়। এসব সংস্কার বাস্তবায় করতে গেলে সরকার অজপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, তাই অনেক দেশ শর্ত মেনে ঋণ েিত চায় না। বাংলাদেশের সাথে শর্তগুলো এখনও চ‚ড়ান্ত না হলেও, প্রাথমিক আলোচনা থেকে জানা যায়, ঋণ পেতে সরকারকে প্রধানত পাঁচটি শর্ত মানতে হবে। শর্তগুলো হল: ১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহ সার্বিক বাজেট ভর্তুকি কমিয়ে আনতে হবে ২. ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি সহ, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে হবে, ৩. কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ৪. মেগা প্রকল্পের স্ব”ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ৫. বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে না। আইএমএফের শর্ত মানতে গিয়ে অনেক স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের বিপদে পড়ার রেকর্ডও আছে। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এবং কর ব্যবহার সংস্কার করা হলে, দেশের অর্থনীতি লাভবান হতে পারে। তবে সুদহার বৃদ্ধি এবং ভর্তুকি প্রত্যাহার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। যেমন জ্বালানী খাতে ভর্তুকি কমালে শুধু যানবাহনে নয়, দেশীয় উৎপাদনের প্রতিটি খাতে বিরুপ প্রভাব পড়বে। এক্ষেত্রে আইএমএফের যুক্তি হল, জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে মানুষ কম তেল কিনবে, ফলে দ‚ষণও হবে কম। তখন মানুষ গ্রিন এনার্জির দিকে ঝুঁকবে। কিš‘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে, জ্বালানির বিকল্প তেমন কিছুই নেই। অর্থাৎ, কৃষকের হাতে কিংবা পরিবহন খাতে যখন ডিজেলের বিকল্প দিয়ে উল্টো ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়, তখন বাধ্য হয়ে বেশি দামেই ডিজেল কিনতে হবে। ডিজেলের বাড়তি দাম পোষাতে কৃষিপণের দাম, পরিবহন খরচ, শিল্প কারখানার উৎপাদন খরচ সহ সব কিছুই বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পণ্যের দাম বাড়াবেন, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ ক্রেতাদের ওপর। এর ফলে ম‚ল্যস্ফীতি আরও বেড়ে যাবে। আইএমএফের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার বাড়ানো। এক্ষেত্রে আইএমএফের যুক্তি হ”েছ, সুদের হার যত বাড়বে, মানুষ ব্যাংক থেকে তত কম ঋণ নিবে। ফলে বাজারে চাহিদা কমে যাবে, চাহিদার বিপরীতে জোগান কমে এলে, ম‚ল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সুদের হার বাড়ালে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। তখন অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে বেকারে পরিণত হবে। সেই পরি¯ি’তিতে একচেটিয়া মুনাফালোভী কোম্পানির কাছে দেশের মানুষ জিম্মি হয়ে পড়বে।
আইএমএফের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তির আগেই সরকার জ্বালানী তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আইএমএফ শুধু জ্বালানী খাতের ভর্তুকী বন্ধ করতে বলেনি; বরং দেশের জ্বালানী তেলের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি সংস্কার করতে বলেছে। বর্তমানে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আদেশে বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়। তবে আইএমএফের পাশাপাশি দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরাও ‘বাজার ম‚ল্যে’ জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতিদিনই বিশ্ববাজারের সাথে জ্বালানী তেলের দাম ওঠা নামা করে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি না থাকার কারণে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে সরকার দেশের মধ্যে দাম বাড়ায়। কিš‘ যখন বিশ্ববাজারে দাম কমে, তখন আর দেশের বাজারে দাম কমায় না। ফলে সাধারন মানুষ কমদামে তেল কেনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে বিগত ৮ বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দেশের মানুষের কাছে বেশি দামে তেল বিক্রি করে ৪৮ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে। অথচ সম্প্রতি তেলের দাম বাড়ানোর পেছনে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশরে লোকসান কে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।