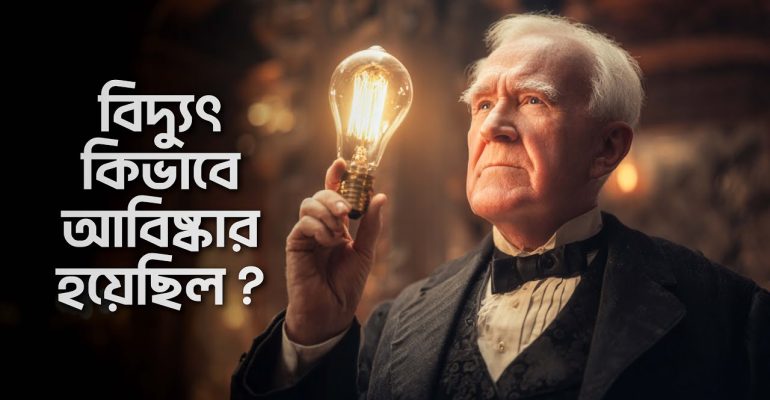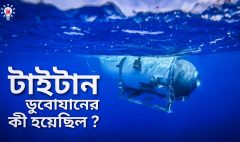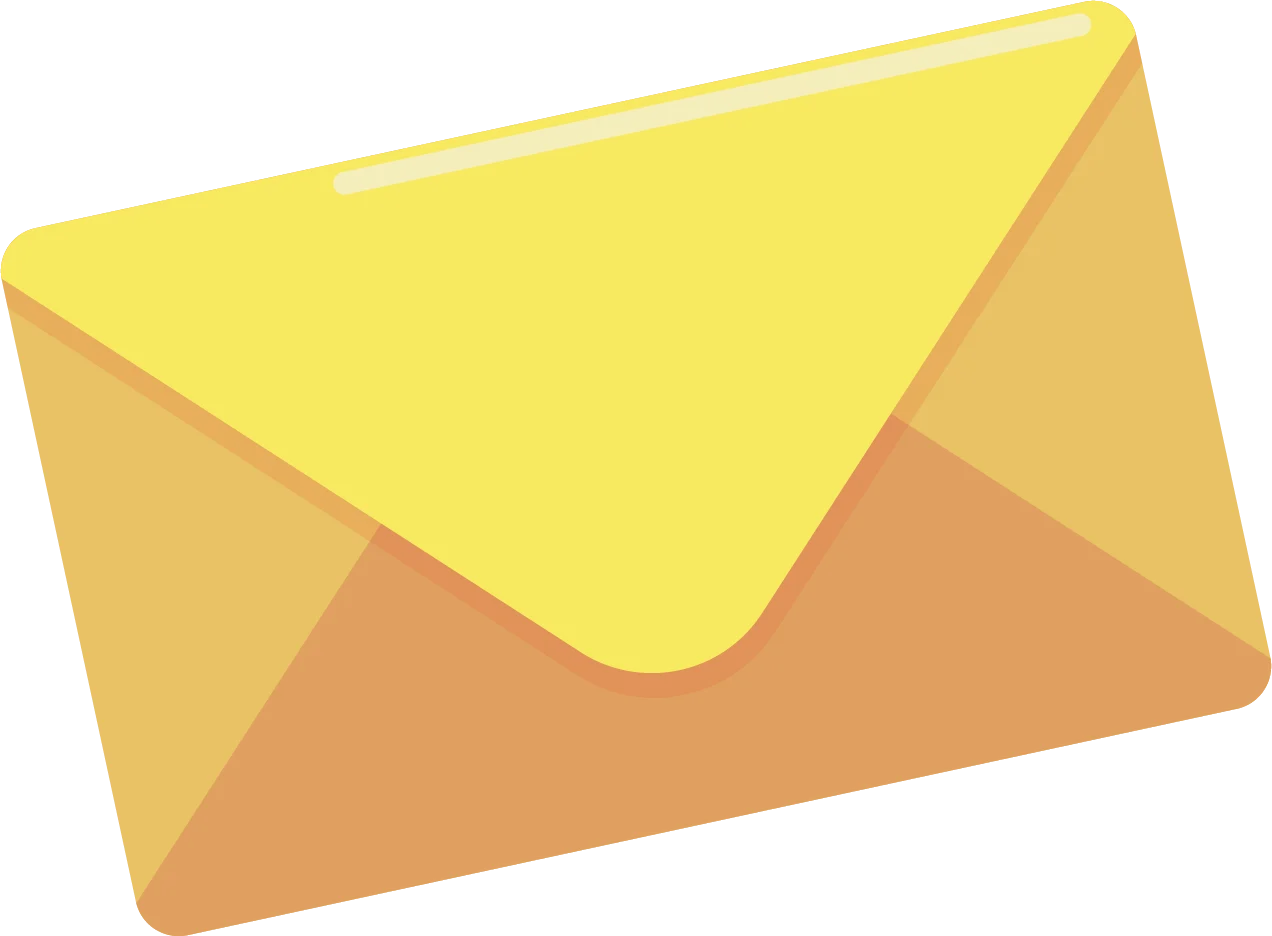বিদ্যুৎ আবিষ্কার
বিদ্যুৎ আবিষ্কার
বিদ্যুৎউদ্ভাবন
খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালের দিকে বিজ্ঞানী থেলিস অফ মিলেটাস লক্ষ্য করলেন যে অ্যাম্বর নামক প্রাকৃতিক রেজিনকে পশমের সাথে ঘষা হলে অ্যাম্বর শুকনো পালককে আকর্ষণ করে। তিনি যেসময় এটি লক্ষ্য করেন সেসময় মানুষ পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে সবকিছুর ব্যাখ্যা করত। যেমন বজ্রপাত হলে মানুষ মনে করত সৃষ্টিকর্তা রাগান্বিত হয়েছেন। এরকম সমাজে বসেই তিনি প্রথম ইলেক্ট্রিসিটির অস্তিত্ব অনুভব করেন যা বর্তমানে স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি বা স্থির তড়িৎ নামে পরিচিত। এখানে যে অ্যাম্বরের কথা বো হচ্ছে, সেটি এসেছে গ্রীক শব্দ ēlektron থেকে। আর সেখান থেকেই ইলেক্ট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ শব্দের উৎপত্তি হয়।
প্রথম বিদ্যুৎ ও ব্যাটারি
বিদ্যুৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনার যাত্রা শুরু হয় ১৬০০ সালের দিকে। উইলিয়াম গিলবার্ট বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করেন। তিনি মূলত অ্যাম্বার, কাঁচ, সালফার প্রভৃতির ঘর্ষণে যে আকর্ষণের সৃষ্টি হয় তা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। আর তিনিই প্রথম এই আকর্ষণকে একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এই ধর্মের নাম দেন electricus।
বজ্রপাত যে আসলেই বিদ্যুৎ তা প্রমাণ করার জন্য ১৭৫২ সালে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা করেন। তিনি ঝড়ের সময় একটি সিল্কের ঘুড়িতে লোহার তার ও ধাতব চাবি যুক্ত করে আকাশে ওড়ান। আকাশে বজ্রপাতের কারণে ঘুড়িতে স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় এবং তিনি প্রমাণ করেন যে বজ্রপাত আসলে বৈদ্যুতিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীতে তিনি বড় বড় দালানকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য lightning rod আবিষ্কার করেন।
১৭৮০ সালের দিকে লুইজি গ্যালভানি নামক একজন ইতালিয়ান জীববিজ্ঞানী ও তাঁর স্ত্রী একটি মৃত ব্যাঙের পায়ের সাথে একটি ধাতব হূক যুক্ত করে লোহার খাঁচায় ঝুলিয়ে রাখেন এবং লক্ষ্য করেন যে ব্যাঙের পা নড়ছে। তিনি প্রথমে ভাবলেন যে ব্যাঙের পা থেকে হয়ত বিদ্যুৎ আসছে, যা ব্যাঙের পা নাড়াচ্ছে। তাই তিনি এটির নাম দেন Animal Electricity বা প্রাণীজ বিদ্যুৎ। তবে বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টা এই ব্যাখার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি ধারণা করেন যে, ব্যাঙের পেশির নড়াচড়ার পেছনে রয়েছে দুটি ভিন্ন ধাতুর সংযোগ। ভোল্টা পরবর্তীতে একটি গবেষণায় দেখান, যখন পরস্পর সংযুক্ত দুটি ধাতু এবং তাদের মাঝে লবণের পানি বা এসিডের মত তরল থাকে তখন সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয়। এই ধারণা মাথায় নিয়ে পরবর্তীতে তিনি Voltaic Pile নামক বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তৈরি করেন।
আলেসান্দ্রো ভোল্টা ১৮০০ সালে রসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী গ্যালভানিক সেল তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক সেল যা DC বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতো। পরবর্তীতে আলেসান্দ্রো ভোল্টার নাম থেকেই তড়িৎবিভবের একক ভোল্ট শব্দটি এসেছে।
প্রথম বিদ্যুৎ ও চৌম্বক
ডেনিশ বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেডই সর্বপ্রথম দেখান যে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকত্ব একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ওয়েরস্টেড মূলত একটি কম্পাসের চারপাশে বৈদ্যুতিক তার স্থাপন করে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেন তখন দেখেন যে কম্পাসের কাঁটাটি ঘুরছে। কাঁটাটির এই ঘূর্ণয়ণ প্রমাণ করে যে সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে চৌম্বকীয় বলের সৃষ্টি হয়েছে।
১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে ওয়েরস্টেডের বিপরীত নীতি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আবিষ্কার করেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী কোনো পরিবাহী তারকে একটি পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্রের মাঝে রাখা হলে একটি তড়িৎচালক বল উৎপন্ন হয়। আর এই তড়িৎচালক বলের কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে জেনারেটর, মোটর, ট্রান্সফরমারসহ অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়।
বাল্ব আবিষ্কার
১৮০২ সালে বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি কার্বন দণ্ডের মাঝে বৈদ্যুতিক স্পার্ক সৃষ্টি করেন যা ছিল অনেক উজ্জ্বল। এখানে মূলত পাশাপাশি থাকা দুইটি কার্বন দণ্ডের মাঝে শক্তিশালী ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC) প্রবাহিত করা হত যা রড দুটির মাঝে একটি আর্ক বা স্পার্ক তৈরি করতো। আর এই প্রযুক্তিকে বলা হয় Arc Lamp। তবে এটি বাসা-বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না।
পরবর্তীতে ওয়ারেন ডি লা রু ১৮৪১ সালে ভ্যাকুয়াম টিউবের ভেতরে প্লাটিনামের ফিলামেন্ট দিয়ে বাল্ব তৈরি করেন। তবে প্লাটিনাম খুব দামি হওয়ায় বাজারে ছড়ানো যায়নি। এর কিছু সময় পর জোসেফ সুয়ান কার্বনাইজড কাগজ ব্যবহার করে ফিলামেন্ট তৈরি করেন। ১৮৭৮ সালে তাঁর তৈরি বাল্ব কার্যকরভাবে আলো দিতে সক্ষম হয়। তিনি এই আবিষ্কারের জন্য যুক্তরাজ্যে পেটেন্টও নেন।
তবে ১৮৭৯ সালে থমাস এডিসন একটি উন্নতমানের কার্বন ফিলামেন্ট বাল্ব তৈরি করেন, যা প্রায় ১৩.৫ ঘণ্টা ধরে জ্বলতে পারত। তবে পরে ১৮৮০ সালে তিনি এমন আরেকটি ফিলামেন্ট তৈরি করেন যা একটানা প্রায় ১২০০ ঘণ্টা পর্যন্ত জ্বলতে সক্ষম ছিল। এরপর তিনি বাল্বকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জ্বালানোর সপ্ন দেখেন। কিন্তু সমস্যা ছিল সবার বাসায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এডিসন সফল বিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি একজন ধূর্ত ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি ১৮৮২ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করেন, যেখানে ডিসি কারেন্ট উৎপাদন করা হত। আর এখান থেকেই এডিসন বিভিন্ন বাসাবাড়ি এবং শিল্প কারখানাগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত। এডিসন শিল্প কারখানাগুলোর জন্য বাসাবাড়ির চেয়ে তিনগুণ বেশি দাম রাখত।
এডিসনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি মূল সমস্যা হল, এসব কেন্দ্র থেকে মাত্র মাইলের দূর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেত। তাই কিছু দূর পর পর এডিসনকে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হয়েছিল।
নিকোলা টেসলা
থমাস এডিসনের ব্যবসা এক সময় জমজামট হয়ে ওঠে এবং আমেরিকার গন্ডি পেরিয়ে ইউরোপেও পৌছে যায়। ১৮৮২ সালে ফ্রান্সের প্যারিয়ে থাকা এডিসনের এক পাওয়ার হাউসে কাজ করতে আসে ২৮ বছর বয়সি সারবিয়ান যুবক, তাঁর নাম নিকোলা টেসলা।
টেসলা এডিসনের কারখানায় কাজ করতে করতে ডিসি জেনারেটরের বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি খুঁজে পান এবং তিনি সেসব সমস্যার সমাধানও বের করে ফেলেন। ১৮৮৪ সালে টেসলা তাঁর সমাধান নিয়ে এডিসনের সাথে দেখা করতে নিউইয়র্কে যান।
তিনি মূলত এডিসনের ডিসি (DC) কারেন্টের পরিবর্তে অল্টারনাটিভ কারেন্টের বা (AC) ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এডিসন টেসলার আইডিয়াকে অবজ্ঞা করেন। এবং টেসলাকে বলেন তিনি যদি তাঁর ডিসি জেনারেটরকে আরও উন্নত করতে পারেন তবে তিনি তাঁকে ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার দিবেন। পরবর্তীতে টেসলা আরও উন্নত ডিসি জেনারাটরের ধারণা নিয়ে এডিসনের কাছে গেলেও, এডিসন সেই পুরষ্কার দিতে অস্বীকার করে।
এরপর টেসলা এডিসনের কোম্পানি ছেড়ে নিজের কোম্পানি খোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর অল্টারনাটিভ কারেন্টের আইডিয়া নিয়ে আমারিকান উদ্যোক্তা জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে যান। ওয়াশিংটন বুজতে পারেন যে, দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য টেসলার অল্টারনাটিভ কারেন্টই একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা।
জর্জ ওয়াশিংটন টেসলার অল্টারনাটিভ কারেন্টের প্যাটেন্ট ৬০ হাজার ডলারে কিনে নেন। এবং তিনি প্রত্যেক হর্স পাওয়ার বিদ্যুতের জন্য টেসলাকে ২.৫ ডলার রয়েল্টি অফার করেন। আর এখান থেকেই ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং নামে নতুন এক কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়।
এই নতুন কম্পানি বাসাবাড়ি এবং কারখানার জন্য সমান দাম রাখে। এমনকি তারা এডিসনের কম্পানির চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ দাম রাখে। কারণ তাদের উৎপাদন ব্যয় হত অনেক কম। তারা এক জায়গায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ট্রান্সফরমারের সাহায্যে অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাঠাতে পারত। যা DC তে ছিল প্রায় অসম্ভব এবং ব্যয়বহুল।
টেসলার একটি বিশেষত্ব হল তিনি তাঁর আবিষ্কারকে সবসময় উন্নত করার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর AC জেনারেটরেও এমন কিছু পরিবরতন করেন যার ফলে শুধু বাল্ব না অন্যান্য যন্ত্রপাতিও AC বিদ্যুতের মাধ্যমে চালানো সম্ভব হয়। সেকার সকলে অল্টারনাটিভ কারেন্ট একসময় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
বিদ্যুৎ যুদ্ধ
এসি কারেন্টের জনপ্রিয়তার পর টেসলা একদিকে বিপুল মুনাফা করতে থাকে, অন্যদিকে এডিসনের ব্যাপক লোকসান গুনতে হয়। ফলে এডিসন টেসলার অল্টারনাটিভ কারেন্টকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আর সেখান থেকে তৈরী হয় এক তীব্র ব্যবসায়িক লড়াই, ইতিহাসে যাকে বলা হয় The current war।
১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে জন ফিকস নামের এক টেলিগ্রাম লাইনম্যান অসাবধানতাবশত একটি হাই-ভোল্টেজ AC তার স্পর্শ করে, মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। তখন এডিসন মানুষকে বোঝাতে শুরু করে যে, অল্টারনাটিভ কারেন্ট অত্যন্ত বিপদজ্জনক।
AC কারেন্টের ঝুঁকি দেখানোর জন্য এডিসন ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে বিভিন্ন প্রাণিকে মেরে ফেলে। এমনকি তার কোম্পানি সার্কাসের এক হাতিকে ইলেকট্রিক শক দেয় এবং সেটার ভিডিও ধারণ করে প্রচার করতে থাকে।
শুধু তাই নয় তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে AC কারেন্টের ক্ষতি নিয়ে একটি চিঠিও লিখেন। তবে এডিসন এখানেই থেমে থাকেনি। তিনি টেসলার কম্পানিকে নিচুঁ করার জন্য আরও একের পর এক বিভিন্ন অমানবিক ও অন্যায় কাজ করতেই থাকে।
এডিসনের এমন অধপতনের কারণে, তার কোম্পানির পরিচালকেরা সকলের সম্মতিতে এডিসনকেই নিজ কোম্পানি থেকে বের করে দেয়। ১৮৯২ সালে সেই কোম্পানিকে থমসন হিউস্টোন ইলেক্ট্রিক কোম্পানির সাথে যুক্ত করা হয়। আর সেখান থেকেই চালু হয় জেনারেল ইলেক্ট্রিক নামের নতুন এক কম্পানি।
AC বনাম DC ও আধুনিক বিদ্যুৎ
এতক্ষন আমরা এসি, ডিসি বিদ্যুৎ আবিষ্কারের গল্প জানলাম। এবার এই দুই ধরনের বিদ্যুৎ কিভাবে প্রবাহিত হয়, তা বোঝা দরকার। বিদ্যুতের প্রবাহকে পানির পাইপের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহের সাথে তুলনা করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।
DC কারেন্ট হল এমন একটি প্রবাহ যা সব সময় একদিকে চলতে থাকে। মনে করুন, আপনার বাসার পানির ট্যাংক থেকে পানি রান্না ঘরের কলের দিকে যাচ্ছে। এটিই ডিসি কারেন্ট।
অন্যদিকে AC কারেন্ট হল এমন একটি প্রবাহ যা সময়ের সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে। তারমানে মনে করুন, কিছুক্ষণ পানির ট্যাংক থেকে পানি রান্না ঘরের কলের দিকে যাচ্ছে, আবার একটু পরে পানির কল থেকে পানি ট্যাংকের দিকে যাচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী বাসাবাড়িতে এবং আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বিদ্যুৎ সংযোগে মূলত AC কারেন্ট ব্যবহার করা হয়। সরাসরি বৈদ্যুতিক লাইন থেকে চালানো ফ্যান, লাইট, টিভি, ফ্রিজ সবই AC ভিত্তিক।
তবে মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের মত বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আসলে DC কারেন্ট প্রয়োজন হয়। এজন্য এগুলোর সাথে অ্যাডাপ্টার বা চার্জার দেওয়া থাকে, যা ঘরের AC বিদ্যুৎকে DC-তে রূপান্তর করে ডিভাইস চালায় বা ব্যাটারি চার্জ করে।
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশে 220–240 ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপানসহ কিছু দেশে 110–120 ভোল্ট ব্যবহৃত হয়।
240 এর মত উচ্চ ভোল্টেজে শক্তি পরিবহণে কম কারেন্ট লাগে। তাই উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ পরিবহণ অনেক সাশ্রয়ী। অন্যদিকে কম ভোল্টেজ বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য নিরাপদ। 110V-এ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে মৃত্যুর ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম থাকে।