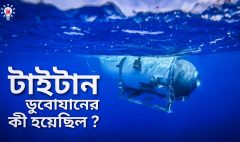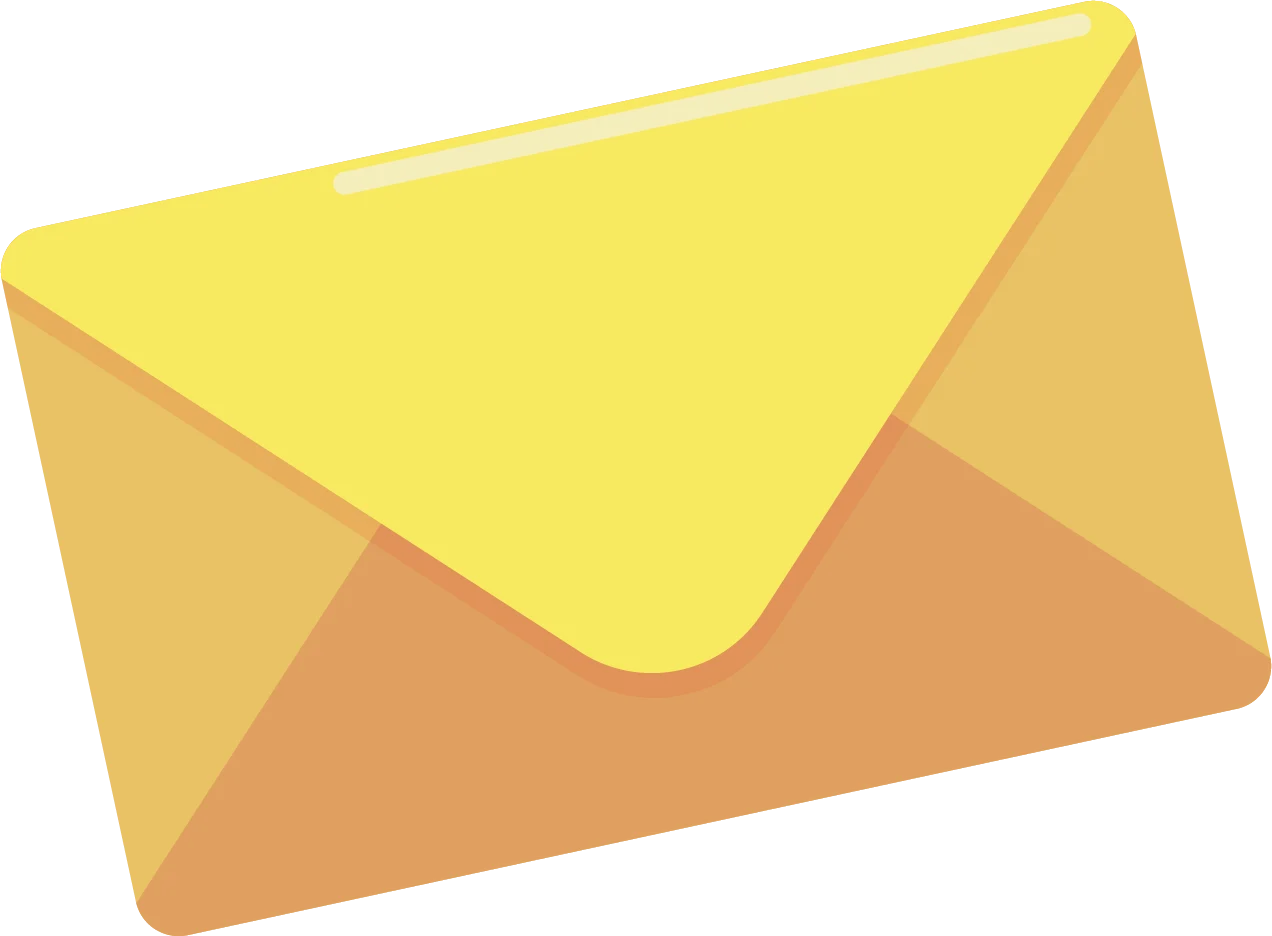ডলারের বিপরীতে দুর্বল টাকা
ডলারের বিপরীতে দুর্বল টাকা
ভূমিকা
২০২১ সালে বংলাদেশের আমদানি কমা ও রেমিট্যান্স বাড়ার কারণে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল। তবে ২০২২–২৩ সালে বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বেড়ে যায়। তখন আমদানি ব্যয় বাড়ায় রিজার্ভ দ্রুত কমতে থাকে।
২০২৪ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশের রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। পরবর্তীতে বেশ কিছু সরকারী নীতি, বৈদেশিক সহায়তা ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ফলে পরিস্থিতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়।
২০২৫ সালে বছরের মাঝামাঝি সময়ে রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৭২ বিলিয়ন ডলার। যা বিগত কয়েক বছরের তুলনায় বেশ ভালো অবস্থানই বলা যায়।
টাকার মান কতটুকু দুর্বল?
২০২২ সালের মাঝামাঝি যেখানে এক ডলারের বিনিময়ে ৮৫–৮৬ টাকা পাওয়া যেত, ২০২৪ সালের শুরুর দিকেই সেটি ১১০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। একই বছরের শেষে সরকারি হিসাবে ডলার দাঁড়ায় প্রায় ১২২ টাকায়। বাংলাদেশ ব্যাংক ধাপে ধাপে অফিসিয়াল বিনিময় হার বাড়িয়েছে; ফলে শুধু ২০২৪ সালেই টাকার মান ১২.৭২% হ্রাস পায়।
তবে ২০২৫ সালে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ডলার প্রায় ১২২ টাকার আশেপাশেই লেনদেন হয়। জুলাইয়ে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। যদিও অতি এটি নগণ্য পরিবর্তনের কারণে, সার্বিকভাবে টাকা এখনও ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল অবস্থাতেই রয়েছে। ইউরো ও ভারতীয় রুপির বিপরীতেও টাকার মানের একই প্রবণতা দেখা গেছে।
ডলার সংকট সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩–২৪ সালে বিভিন্ন বিনিময় হার একীভূত করে “ক্রলিং পেগ” ব্যবস্থা চালু করে। এর ফলে ২০২৪ সালের মে–আগস্টে অফিসিয়াল রেট দ্রুত বাড়ানো হয়, যাতে তা খোলা বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেমন, মে মাসে অফিসিয়াল হার ১১৭ টাকা নির্ধারণ করলে খোলা বাজারে তা লাফিয়ে ১২৫ টাকায় পৌঁছায়। ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়বে ভেবে অনেক মানি এক্সচেঞ্জ তখন ডলার বিক্রি বন্ধ করে দেয়। এতে কালোবাজারে দৌরাত্ন বেড়ে গিয়ে টাকার ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।
বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারি ও রেট সমন্বয়ের ফলে খোলা বাজার ও অফিসিয়াল হারের ব্যবধান কিছুটা কমেছে। তবে চাহিদা বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে আবারও কিছুটা অস্থিরতা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে যখনই ধারণা তৈরি হয় যে টাকার মান আরও কমতে পারে, তখন ব্যবসায়ী থেকে প্রবাসী—অনেকে ডলার জমিয়ে রাখেন, ফলে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি হয়ে টাকার ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি হয়।
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার অবমূল্যায়ন থামেনি কেন?
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সম্প্রতি আবার বেড়েছে। কিন্তু তারপরও টাকার মান আগের মতো শক্তিশালী হয়নি। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, এর পেছনে রয়েছে কয়েকটি আন্তঃসম্পর্কিত দিক।
২০২২–২৩ সালে চলতি হিসাবের বড় ঘাটতি সামাল দিতে রিজার্ভ খরচ করতে হয়েছিল এবং টাকা দ্রুত অবমূল্যায়িত হয়। ফলে বাজারের আস্থা নড়ে যায়। এখন রিজার্ভ বেড়েছে বটে, তবে আগের ক্ষতি কাটিয়ে সেই আস্থা পুরোপুরি ফিরতে সময় লাগছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি। ২০২৪ সালে দেশে বহু বছর পর মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কে ওঠায় টাকার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনলেও তা এখনও লক্ষ্যমাত্রার ওপরে রয়ে গেছে, ফলে বিনিময় হার শক্ত হয়নি।
বাজারের আস্থা ও মনস্তত্ত্বও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বৈশ্বিক অস্থিরতায় অনেকেই ডলার বা স্বর্ণকে নিরাপদ ভেবে টাকা থেকে সরে গেছেন, এতে কৃত্রিম চাপ তৈরি হয়েছে। একই সময়ে রিজার্ভের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। মোট রিজার্ভ বড় হলেও এর একটি অংশ ঋণ বা স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক অর্থ, যা ব্যবহারযোগ্য নয়। নিট রিজার্ভ বাস্তবে ২৫–২৬ বিলিয়নের মধ্যে থাকায় বাজার পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়নি।
অন্যদিকে, নীতিনির্ধারকেরাও টাকার মান কিছুটা দুর্বল রেখেছেন, যাতে রপ্তানিকারকরা বাড়তি সুবিধা পান। এর ফলেই ২০২৪–২৫ অর্থবছরে রপ্তানি ৮.৬% বেড়ে প্রায় ৪৮.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, রিজার্ভ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু টাকার দর ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝামাঝি স্তরে রাখা হয়েছে।
সব মিলিয়ে, অতীতের ঘাটতির চাপ, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, বাজারের আস্থা সংকট, রিজার্ভের গুণগত সীমাবদ্ধতা এবং নীতিগত কারণে টাকা এখনও শক্ত অবস্থায় ফিরতে পারেনি।
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের নীতিগত পদক্ষেপ
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার গত দুই বছরে টাকার অবমূল্যায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকট সামাল দিতে একযোগে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল মুদ্রানীতি কঠোর করা। ২০২৪ সালে নীতিগত সুদের হার কয়েক ধাপে বাড়িয়ে ১০ শতাংশে নেওয়া হয়, যা ঋণ ব্যয়বহুল করে ব্যক্তিখাতের ব্যয় ও আমদানি চাহিদা কমায়। পাশাপাশি বাজার থেকে অতিরিক্ত তারল্য টেনে নেওয়া হয়, যাতে অযথা ডলার কেনাবেচার চাপ না পড়ে।
বিনিময় হারেও আনা হয় সংস্কার। পুরনো স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ধাপে ধাপে আংশিক ভাসমান হার চালু করে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় প্রতিদিন সামান্য করে ধীরে ধীরে ডলারের দাম ১১০ থেকে ১২০ টাকার ওপরে ওঠানো হয়।
অন্যদিকে, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ কমাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তুকি সমন্বয় করা হয়। জ্বালানি তেলের ভর্তুকি কমানো, বিলাসপণ্য ও গাড়ি আমদানিতে কঠোর এলসি মার্জিন আরোপের ফলে ২০২৩–২৪ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ১১ শতাংশ কমে যায়। পরের বছরে কিছুটা শিথিলতা এলেও বৃদ্ধি হয় মাত্র ২.৪ শতাংশ।
রাজস্ব ও বাজেট ব্যবস্থায় নেওয়া হয় সংযমী নীতি। অপ্রয়োজনীয় উন্নয়ন ব্যয় কমানো, ভর্তুকি হ্রাস, আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট থেকে রাজস্ব বাড়ানোর পাশাপাশি আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির কাছ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা নিশ্চিত করা হয়, যা রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
সবশেষে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়াতে ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা চালু রাখা হয় এবং ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক হার দিতে উৎসাহিত করা হয়। হুন্ডি প্রতিরোধে কঠোর অভিযান চালানো হয়। ফলে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে প্রতি মাসেই ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স দেশে আসে, আর ২০২৫ অর্থবছরে তা রেকর্ড ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়।
সব মিলিয়ে এই পদক্ষেপগুলো টাকার ওপর চাপ কমিয়েছে। রিজার্ভ আবার বাড়ছে, আমদানি–রপ্তানি ভারসাম্য কিছুটা ফিরেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারও আপাতত স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করছে।
রেমিট্যান্স, রপ্তানি, আমদানি ও চলতি হিসাবের ভূমিকা
বাংলাদেশের টাকার মান মূলত বৈদেশিক আয়—যেমন রেমিট্যান্স ও রপ্তানি—এবং ব্যয়—যেমন আমদানি ও ঋণ পরিশোধ—এর ওঠানামার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। সাম্প্রতিক সময়ে এ উপাদানগুলো মিলেই টাকার ওপর চাপ কিছুটা লাঘব করেছে।
২০২৪–২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্স রেকর্ড পরিমাণে বেড়ে প্রায় ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২৭% বেশি। ২০২৫ সালের মার্চ মাসেই এককভাবে ৩.২৯ বিলিয়ন ডলার দেশে এসেছে, যা ইতিহাসের সর্বোচ্চ। এই প্রবাহ শুধু রিজার্ভ বাড়ায়নি, ব্যাংকগুলোর ডলার লেনদেন সহজ করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতেও ব্যয় ও উৎপাদন বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মন্দার কারণে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ২০২৪–২৫ সালে তা ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮.৬% বেড়ে ৪৮.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমে ২০.৫ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে, যা টাকার ওপর চাপ কমিয়েছে।
আমদানির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে। ২০২৩–২৪ সালে আমদানি ১০.৬% কমে যায় এবং পরের বছরে মাত্র ২–৩% বৃদ্ধি পায়। যদিও মেশিনারি ও কাঁচামালের কম আমদানি অর্থনীতির স্থবিরতার ইঙ্গিত দেয়, স্বল্পমেয়াদে এটি ডলারের চাহিদা কমিয়ে টাকার সাপোর্ট দিয়েছে।
বাজারে জল্পনা-কল্পনা ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময়হার
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ডলার সংকটে স্পষ্ট হয়েছে যে টাকার মান শুধু রিজার্ভ বা আনুষ্ঠানিক নীতির ওপর নির্ভর করে না; বাজারের জল্পনা ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারও বড় ভূমিকা রাখে। ২০২২–২৩ সালে ব্যাংকে ডলার না পেয়ে আমদানিকারক ও ভ্রমণকারীরা খোলা বাজারে গেলে দাম লাফিয়ে ওঠে। এক সময় অফিসিয়াল রেট যখন ১১৫–১১৭ টাকার মধ্যে ছিল, তখন খোলা বাজারে ১২৫–১২৮ টাকা পর্যন্ত গিয়েছিল। এতে সাধারণ মানুষও সন্দিহান হয়ে পড়ে—অনেকে হুন্ডিতে বেশি দাম পেতে ব্যাংক এড়িয়ে গেছেন। আবার ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়বে ভেবে বেশি দরে ডলার মজুত করেছেন। এর ফলে মানুষ যত বেশি ডলার কিনেছে, তত টাকার দর কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪ সালে ধাপে ধাপে টাকার মান কমিয়ে অফিসিয়াল ও খোলা বাজারের ফারাক কমায়। এতে হুন্ডির আকর্ষণ কমে যায় এবং ২০২৫ নাগাদ প্রবাসীরা আবার ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে উৎসাহী হন। তবে ৫ আগষ্টের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘনীভূত হলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ডলার শিগগিরই ১৩০ টাকার ওপরে যাবে।
তখন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিষ্কার জানিয়েছিল যে, বিনিময় হার স্থিতিশীল আছে, তারপরও বাজারে পুরোপুরি আস্থা ফিরতে সময় লেগেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, তথ্যের স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীল নীতি না থাকলে এবং রিজার্ভ বাড়লেও শুধু গুজবের জেরেই টাকা আবার দুর্বল হয়ে যেতে পারে।