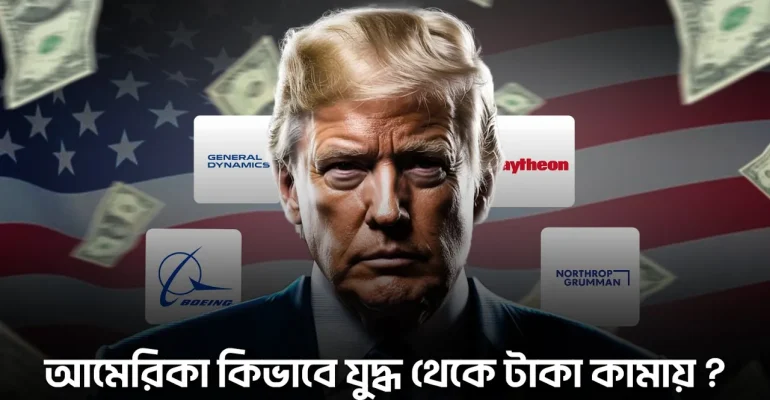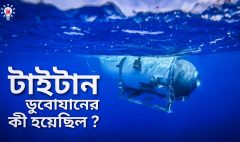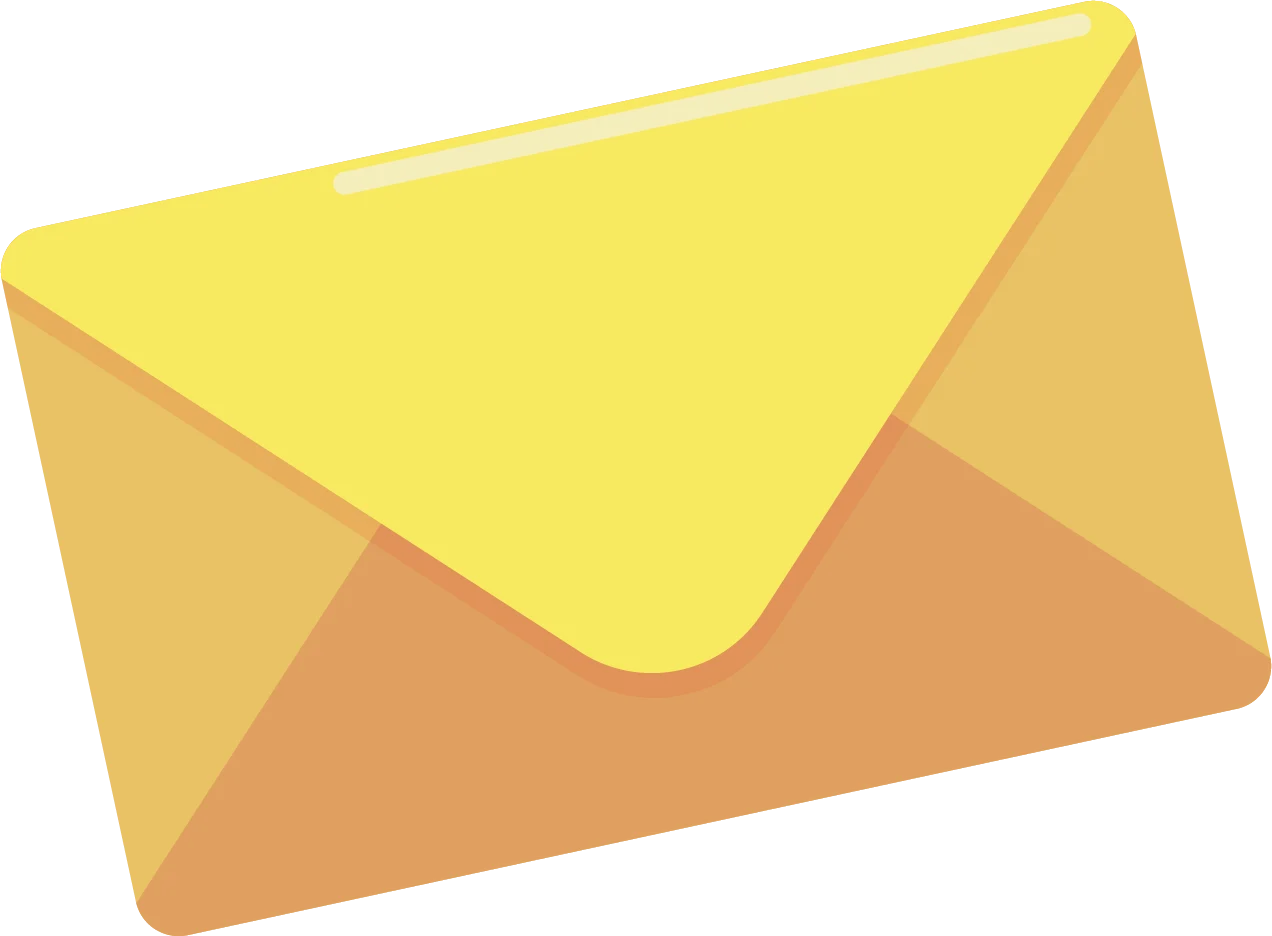আমেরিকার যুদ্ধ ব্যবসা
আমেরিকার যুদ্ধ ব্যবসা
ভূমিকা
যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সামরিক শক্তিধর দেশ হলেও, বিগত কয়েক দশকে তারা যতগুলো যুদ্ধ করেছে, তার প্রায় অধিকাংশ যুদ্ধেই যুক্তরাষ্ট্র হেরেছে। ভিয়েনমান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ বা আফগানিস্তান যুদ্ধ আমেরিকার পরাজয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রায় প্রতিটি যুদ্ধ থেকেই আমেরিকা অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধ একটি “পরম বিপর্যয়” হলেও মার্কিন সামরিক ঠিকাদারদের জন্য এটি ছিল একটি বাজিমাৎ করা প্রকল্প। এমনকি গাজা এবং ইউক্রেনের যুদ্ধে সরাসরি মার্কিন সৈন্য না থাকলেও, এই যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল মুনাফা করেছে।
সেকারণেই মূলত আমেরিকানরা যুদ্ধকে নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে নির্মম হত্যাযজ্ঞ হিসেবে নয়; বরং অবাধে বিপুল টাকা কামানোর লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দেখে। এই বিষয়টির পোশাকী নাম হল Military-Industrial Complex, সংক্ষেপে MIC। যুদ্ধে হারজিৎ যাই হোক না কেন, আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ীরা সবসময়ই বিজয়ী হয়।
সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স
১৯৬০-এর দশকের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ার তাঁর বিদায়ী ভাষণে এক ঐতিহাসিক সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমেরিকার নিরাপত্তা আর অর্থনীতি রক্ষার জন্য যে বিশাল সামরিক যন্ত্র তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে অস্ত্র শিল্পের অদৃশ্য এক বন্ধন তৈরি হচ্ছে। এই বন্ধনকে তিনি Military-Industrial Complex বা “সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স” নামে ডাকেন।
আইজেনহাওয়ার ভয় পেয়েছিলেন, এই শক্তিশালী জোট যদি “অযাচিত প্রভাব” অথবা অতিরিক্ত ক্ষমতা পেয়ে যায়, তাহলে মার্কিন গণতন্ত্রই বিপদের মুখে পড়তে পারে। সময়ের সঙ্গে তাঁর সেই আশঙ্কা যে কতটা সত্যি হয়ে উঠেছে, তা আজকের বাস্তবতায় স্পষ্ট।
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স শুধু অস্ত্র বানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতেও বড় ভূমিকা রাখে। ২০২৩ সালে দেখা গেছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলো প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে, যার মধ্যে রেকর্ড ৭৬৫ বিলিয়ন ডলার এসেছে সরাসরি সরকারি চুক্তি থেকে। অর্থাৎ মার্কিন সরকার নিজেই এইসব অস্ত্র কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে বড় ক্রেতা।
যুক্তরাষ্ট্র যখন ইসরায়েল কিংবা ইউক্রেনের মতো দেশে সামরিক সাহায্য পাঠায়, তখন অনেকেই ভাবেন, সেই টাকা হয়তো সরাসরি সেই দেশের সরকারের হাতে যায়। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি মোটেও সেরকম নয়। যুক্তরাষ্ট্রের েদওয়া আর্থিক বা সামরিক সহায়তার বড় অংশই ফিরে আসে আমেরিকান অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলোর পকেটে। তারমানে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সেদেশের সাধারণ মানুষের করের টাকা পরোক্ষভাবে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়িদের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।
রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার এক বছরের মাথায়, মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল ডাইনামিক্সের (General Dynamics) শেয়ারের দাম প্রায় ৩৪ শতাংশ বেড়ে যায়। তারপর ইসরায়েল গাজায় হামলা শুরু করার পর আরেক মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা জায়ান্ট লকহিড মার্টিনের (Lockheed Martin) শেয়ারের দাম ৫৪ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যায়। গাজা এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ চলাকালীন রেথিয়ন (Raytheon), বোয়িং (Boeing), নর্থরপ গ্রুম্যান (Northrop Grumman) এর মতো সামরিক প্রতিরক্ষা সামগ্রী কোম্পানিগুলোর শেয়ারমূল্য এবং মুনাফাও আকাশ ছুঁয়েছে।
১৯৪৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিদেশি সাহায্য দিয়েছে, যা অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে ঘটেনি। কিন্তু সেই অর্থও শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলকে বলা হয়, এই টাকার বড় অংশ আমেরিকান কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র কিনতেই খরচ করতে হবে। ফলে সেই অর্থ আবার ফিরে আসে লকহিড মার্টিন, রেথিয়ন বা বোয়িং-এর মতো কোম্পানিগুলোর কাছে।
হামাস, হিজবুল্লাহ, হুথি বা ইরান যে পক্ষ থেকেই ইসরায়েলের মিসাইল ছোড়া হোক না কেন, তাতে সবচেয়ে বেশি খুশি আর লাভবান যুক্তরাষ্ট্রের রেথিয়ন। কারণ তারাই ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সরঞ্জাম সরবারাহ করে।
বিগ ভাইভ
যুক্তরাষ্ট্র একাই পুরো বিশ্বের প্রায় অর্ধেক অস্ত্র সরবরাহ করে, অর্থাৎ বিশ্বের মোট অস্ত্রের প্রায় ৫০ শতাংশই আসে আমেরিকার কাছ থেকে।
এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি মার্কিন কোম্পানি পুরো বিশ্বের প্রতিরক্ষা শিল্পের ওপর প্রায় একচেটিয়া দখল করে বসে আছে। এরা হলো লকহিড মার্টিন, রেথিয়ন, বোয়িং, নর্থরপ গ্রুম্যান আর জেনারেল ডাইনামিক্স। এদের এসাথে বলা হয় বিগ ফাইভ। বিগ ফাইভের আধিপত্য বিস্তারের মূল লক্ষ্য হল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বড় যুদ্ধ থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করা।
অনেকেই ভাবে, যুক্তরাষ্ট্র হয়ত যুদ্ধ জেতার জন্য লড়াই করে, কিন্তু বাস্তবে তারা চায় যুদ্ধ যেন শেষ না হয়, এবং অনন্তকাল যুদ্ধ চলতেই থাকে। আমেরিকার ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধ হল আফগানিস্তান যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ ছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা কম্পানিগুলোর জন্য অন্তহীন মুনাফার ব্যবসায়িক মডেল। অথচ আফগানিস্তান থেকে শেষ পর্যন্ত সেনা ফিরিয়ে আনার পরও দেখা গেছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট একটুও কমেনি, বরং তিন বছরের মধ্যে প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। এভাবে বিশ্বের বড় কোন যুদ্ধ বন্ধ হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট কমে না, বরং বাড়তেই থাকে।
১৯৯০-এর দশকে, রাশিয়ার সাথে শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, মার্কিন সরকার ভাবছিল তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট কমানো দরকার। সেসময় যুক্তরাষ্ট্রে ৫১টি আলাদা আলাদা প্রতিরক্ষা কোম্পানি ছিল। মার্কিন সরকারের ইচ্ছা ছিল এগুলোকে একীভূত করে কমসংখ্যক, কিন্তু বড় এবং আরও শক্তিশালী কোম্পানি তৈরি করা। সেই উদ্দেশ্যে পেন্টাগন ১৯৯৩ সালে শীর্ষ প্রতিরক্ষা নির্বাহীদের এক নৈশভোজে ডাকে, যা পরবর্তীতে কুখ্যাত “লাস্ট সাপার” নামে পরিচিত হয়।
সেই ডিনারের পর থেকেই বড় বড় অস্ত্র কোম্পানিগুলো একীভূত হয়ে জন্ম নেয় “বিগ ফাইভ”। সেই থেকে বিগ ফাইভ শুধু মার্কিন অর্থনীতির টুটিই চেপে ধরেনি। বরং তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি কাজে সরকারি সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশে যুদ্ধ করবে, কোথায় যুদ্ধে মধ্যস্থতা করবে, এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বা আচরণ কেমন হবে সেসব বিষয়ও ঠিক করে দেয় বিগ ফাইভ।
অথচ এসব অস্ত্র নির্মাতা কম্পানিগুলো নিজেদের কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন তারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে, মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে, এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত এদের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন –
“এবং যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করনা তখন তারা বলেঃ আমরাতো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী।” – আল কুরআন (সুরা বাকারা, আয়াত ১১)
ন্যাটো সম্প্রসারণ
বিগ ফাইভ কম্পানির বিশাল সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স শুধু অস্ত্র তৈরি করেই থেমে থাকে না, বরং তারা নিজেদের ব্যবসার নতুন বাজার খুঁজে পেতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা ষড়যন্ত্রের সাথেও জড়িত থাকে।
বিগ ফাইভ ন্যাটো সম্প্রসারণের পক্ষে ব্যাপক লবিং করে, কারণ নতুন কোনো দেশ যখন ন্যাটোর সদস্য হয়, তখন শর্ত অনুযায়ী সেই দেশের সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন করতে হয়। আর অাধুনিকায়ন মানেই হলো বিপুল পরিমাণে নতুন অস্ত্র কেনা। সাধারণত ন্যাটো সদস্যদের সেই অস্ত্রও যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর কাছ থেকেই কিনতে হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো জোটের মোট অস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে। এভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আর অস্ত্র ব্যবসা একে অন্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।
মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে প্রতি বছর শত শত লবিস্ট নিয়োগ করে। ধারনা করা হয় বর্তমানে প্রায় সাত শতাধিক লবিষ্ট আছে। তারমানে মার্কিন কংগ্রেসের প্রায় প্রতিটি সদস্যের জন্য একজনের বেশি লবিস্ট দাঁড় করিয়ে রাখে তারা।
ফলে কংগ্রেসে যখনই প্রতিরক্ষা নীতি বা বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়, তখন এই লবিস্টরা প্রকাশ্যে এবং গোপনে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর তথ্য হলো, মার্কিন কংগ্রেসে যেসকল বিশেষজ্ঞরা গিয়ে সাক্ষ্য দেন, তাদের প্রায় ৮০ শতাংশই সরাসরি অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানির পক্ষে লবি করার জন্য টাকা পান। তাই যেসব নীতিকে আমেরিকার সাধারণ মানুষ দেশের নিরাপত্তা নীতি বলে জানে, তার প্রায় অধিকাংশই অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সুগভীর স্বার্থ বিবেচনা করে নেওয়া হয়। আর এই ব্যবসায়িক স্বার্থ শুধু রাজনীতিবিদ বা লবিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামরিক বাহিনীর ভেতরেও ঢুকে পড়েছে।
মার্কিন সেনা বাহিনীর মধ্যে এমন এক প্রোগ্রাম চালু আছে, যেখানে শত শত শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা বড় বড় অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করেন। তারপর তারা আবার সেনাবাহিনীর সামরিক পদে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে অস্ত্র কম্পানির স্বার্থে কাজ করে। এ ছাড়া অনেক উচ্চ-পদস্থ প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা অবসর নেওয়ার পর “বিগ ফাইভ” এর নীতি নির্ধারনী পদে চাকরি পান। ফলে মার্কিন সামরিক বাহিনী আর অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলোর মধ্যে এখন আর কোন আলাদা সীমারেখা নেই। তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে।