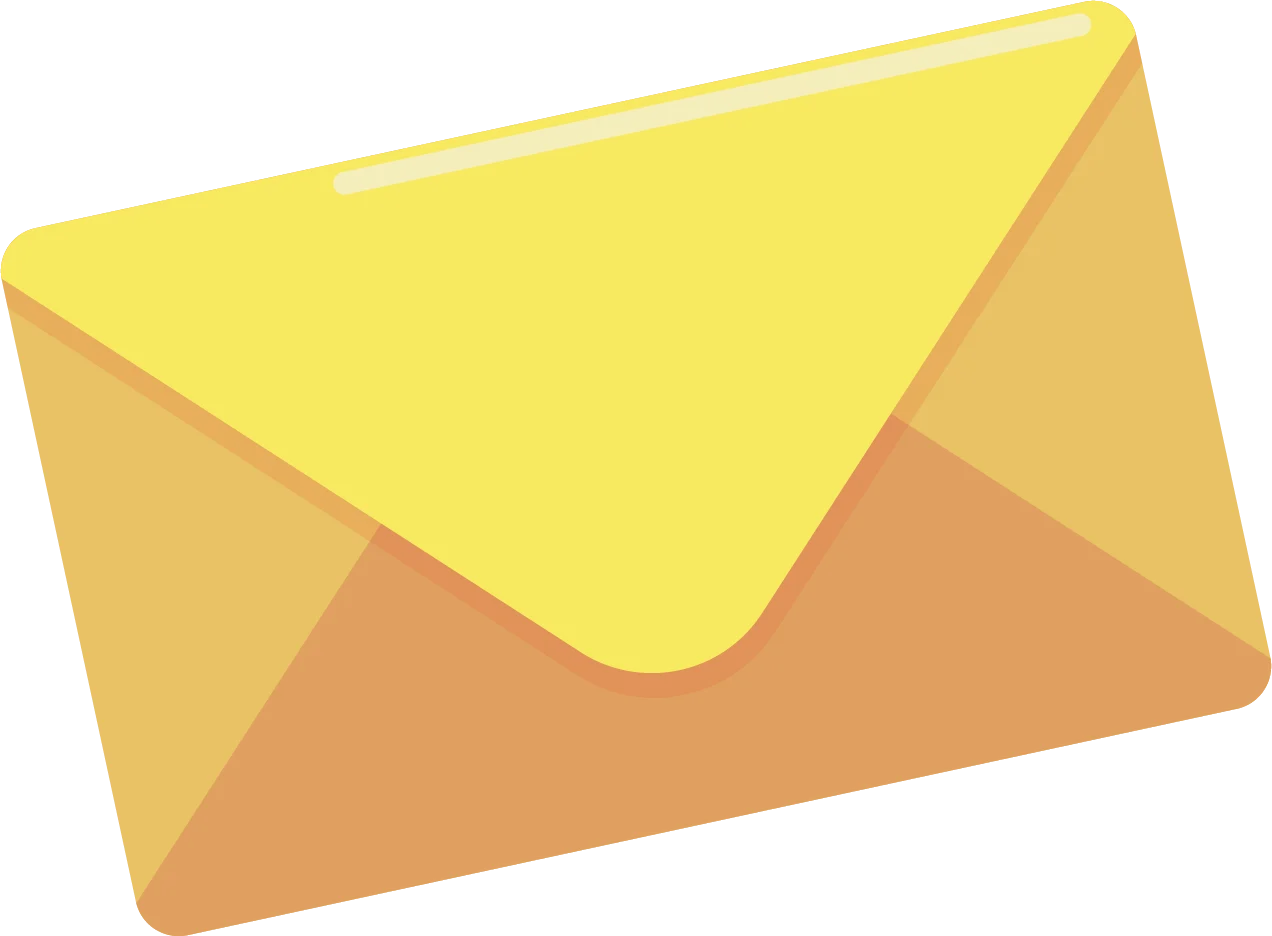ভারত চাঁদে যাচ্ছে কেন
ভারত চাঁদে যাচ্ছে কেন
ভারতের চন্দ্রাভিযান
সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO চন্দ্রযান-৩ নামের একটি মহাকাশ যান উৎক্ষেপণ করেছে। এটি চাঁদের উদ্দেশ্যে ভারতের তৃতীয় অভিযান। চন্দ্রযান-৩ এর গন্তব্য চাঁদের দক্ষিণ মেরু। এই যাত্রায় তাদের চাঁদে পৌছাতে সময় লাগবে ৪০ দিন। চন্দ্রযান-৩ এর অভিযান সফল হলে ভারত হবে চাঁদের বুকে অবতরণ করা চতুর্থ দেশ। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন চাঁদে নামতে সফল হয়েছে।
ISRO
ভারতের মহাকাশ গবেষণার স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং পথিকৃত ছিলেন বিক্রম সারাভাই। ১৯৫০ এর দশকে বিক্রম সারাভাই এর লক্ষ ছিল যে মহাকাশ গবেষণায় ভারত কে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সেজন্য ভারতের প্রথমেই দরকার ছিল একটি মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে মহাকাশ গবেষণা অতটা জরুরী ছিল না। ব্যাপারটা স্বাভাবিকও ছিল কারণ তখন ভারতে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, সীমান্ত সংঘাত সহ নানা বিষয় মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। সকল ধরনের বাঁধা সত্ত্বেও বিক্রম সারাভাই বিজ্ঞানীদের একটি দল তৈরী করলেন এবং দক্ষিণ কেরালায় রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬১ সালে জওহরলাল নেহরু ভারতের মহাকাশ গবেষণার দ্বায়িত্ব ভারতের এটমিক এনার্জি বিভাগের হাতে ছেড়ে দেন। তৎকালীন সময়ে এই বিভাগের সচিব ছিলেন হোমি ভাবা। হোমি ভাবা পরের বছর বিক্রম সারাভাই কে চেয়ারম্যান করে The Indian National Committee for Space Research বা INCOSPAR নামের একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সেই INCOSPAR ই Indian Space Research Organisation বা ISRO হিসেবে রূপান্তরিত হয়। ISRO ১৯৬৩ সালে থাম্বা নামের ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ যাত্রার সূচনা ঘটায়।
চন্দ্রযান ৩
২০০৮ সালে ISRO চন্দ্রযান-১ উৎক্ষেপণ করেছিল। যে মহাকাশ সংস্থা একসময় বাইসাইকেলে করে রকেটের যন্ত্রাংশ পরিবহণ করত, তারা যখন চাঁদের উদ্দেশ্যে পুরোদস্তুর একটি মাহাকাশ যান উৎক্ষেপণ করল তখন পুরো বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অভিযান সফল হবার পর, ISRO মঙ্গল অভিযান এবং চন্দ্রযান-২ মিশন সম্পন্ন করে।
পরবর্তীতে ISRO একটি রকেটে সবচেয়ে বেশি স্যাটেলাইট প্রেরণ করে বিশ্বরেকর্ড করে ফেলে, যা টানা ৪ বছর অটুট ছিল। ISRO ৫ বছরে ১৯টি দেশের ১৭৭ টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ১৪ জুলাই ISRO মহাকাশে পাঠিয়েছে চন্দ্রযান-৩। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে চাঁদের দিকে রওনা দিয়েছে চন্দ্রযান ৩। একটি এলভিএম-৩ রকেট দিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রযানটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এবারের চন্দ্র অভিযানে থাকছে একটি ল্যাণ্ডার ও একটি রোভার। ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাইয়ের নামে ল্যাণ্ডারটির নাম রাখা হয়েছে ‘বিক্রম’ আর রোভারটির নাম ‘প্রজ্ঞান’। ল্যাণ্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে আর রোভার চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করবে। ল্যাণ্ডারটি অগাস্টের ২৩-২৪ তারিখে চাঁদের পিঠে নামার কথা। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা
২০১৯ সালে, চন্দ্রযান ২ ঠিক চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সময়ে ল্যাণ্ডার-রোভারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে চন্দ্রযান ২ এর সেই অরবিটার এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বেস-স্টেশনে নিয়মিত তথ্য পাঠিয়ে চলেছে। চন্দ্রযান ৩ অভিযানেও চন্দ্রযান ২ এর ওই অরবিটারটিকেই ব্যবহার করা হবে বলে ইসরো জানিয়েছে। তৃতীয় চন্দ্রাভিযানে ল্যাণ্ডার-রোভারটির অবতরণ করার কথা চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে, যে জায়গাটি সম্বন্ধে এখনও বিস্তারিত জানা যায় না। এই অঞ্চলে কোন চন্দ্রযান অবতরণ করানো খুবই কঠিন একটি কাজ। সাধারণত চাঁদের বিষুব রেখা অঞ্চলটি নিরাপদে অবতরণের জন্য আদর্শ, কিন্তু ওই অঞ্চল নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক গবেষণা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অঞ্চলেই তাদের সকল অভিযান পরিচালনা করেছে।
চাঁদে অবতরণের জন্য ভারেত সবচেয়ে কঠিন অংশটি বেঁেছ নেওয়ার পেছনে তাদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক স্বার্থ আছে। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্ভাবনাও এই অঞ্চলেই বেশি। ভারত যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে চায় তাহলে তাদেরকে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মতো কোনও অঞ্চলেই যেতে হবে। কিন্তু সেখানে অবতরণের ঝুঁকিটাও অনেক বেশি। চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই দক্ষিণ মেরু অংশেই ২০০৮ সালে জলের সন্ধান পেয়েছিল চন্দ্রযান-১।
৪০ দিন সময় লাগবে কেন?
উৎক্ষেপণের ৪০ দিন পরে চাঁদের মাটিতে নামার কথা ল্যাণ্ডার বিক্রমের। চন্দ্রযান ১ সময় নিয়েছিল ৭৭ দিন আর চন্দ্রযান ২ এর লেগে ছিল ৪৮ দিন। অথচ, নাসার প্রথম মনুষ্যবাহী চন্দ্রযান অ্যাপোলো ১১ মাত্র চার দিনেই চাঁদের পৌঁছে গিয়েছিল। অ্যাপোলোর তিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসেন উৎক্ষেপণের আট দিনের মাথায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ১৯৬৯ সালে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে আমেরিকানরা সময় নিয়েছিল মাত্র চার দিন, ৫০ বছর পরে এসেও কেন সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে ভারতীয়দের ৪০ দিন সময় লাগছে? এর পেছনের মূল কারণ হল বাজেট। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা অত্যন্ত সস্তায় মহাকাশ অভিযান পরিচালনার জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। ভারতের চন্দ্রযান ৩ মিশনের খরচ ধরা হয়েছে মাত্র ৬৫০ কোটি রুপি। বলিউডের বেশ কিছু সিনেমারও এই পরিমাণ বাজেট থাকে। নাসার ১৯৬৯ সালে চাঁদে যেতে খরচ করেছিল ৩৫৫ মিলিয়ন ডলার; যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১২ হাজার কোটি রুপির কাছাকাছি। এছাড়া নাসার মঙ্গল গ্রহ অভিযানের জন্য খরচ হয়েছিল ৬৭১ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ইসরোর মঙ্গল অভিযানের খরচ মাত্র ৭৪ মিলিয়ন ডলার।
মার্কিনরা চাঁদে যাওয়ার সময় জ্বালানি সহ অ্যাপোলো ১১ ওজন ছিল প্রায় ২ হাজার ৮০০ টন, কিন্তু ইসরো যে রকেট উৎক্ষেপণ করেছে তার জ্বালানি সহ ওজন মাত্র ৬৪০ টন। অ্যাপোলো ১১র মোট ওজনের ৮০ শতাংশই ছিল জ্বালানি। অ্যাপোলোর ল্যাণ্ডার ঈগল চাঁদে অবতরণ করতে, চাঁদের বুকে গবেষণা করতে, ল্যান্ডার যান অরবিটারে ফিরে আসতে এবং সবশেষে পৃথিবীতে ফিরে আসতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির দরকার ছিল। অন্যদিকে ইসরো চেষ্টা করছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে, খুব সামান্য পরিমাণ জ্বালানি খরচ করেই যেন তারা চাঁদে পৌছাতে পারে। এই পদ্ধতির কারণে, রকেটটি সরাসরি চাঁদের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে এটি পৃথিবীর চারপাশে একটি দীর্ঘ বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে। তারপরে ধীরে ধীরে চন্দ্রযানটি চাঁদের দিকে আগাতে থাকবে এবং বক পর্যায়ে চাঁেদ অবতরণ করবে। আর সে কারণেই চন্দ্রযান ৩ চাঁদে পৌছাতে অ্যাপোলো ১১ এর তুলনায় প্রায় দশগুণ সময় বেশি নেবে।
চন্দ্রযান-৩ এর কাজ কী?
ভারত চাঁদের বুকে যে রোভার অবতরণ করাবে, সেটিতে মূলত পাঁচটি যন্ত্র থাকবে। এসব যন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল চাঁদের মাটির প্রাকৃতিক চরিত্র অনুসন্ধান করা, এর আশে পাশের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করা এবং চাঁদের মাটির নীচে কী হচ্ছে তা খুঁজে দেখা। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আশা করছেন তারা নিশ্চই নতুন কিছু খুঁজে পাবেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাঁদের বয়স আবিষ্কারেরও চেষ্টা হবে বলে ইসরোর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। তবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু হল এমন এক এলাকা, যেখানে কখনও সূর্যের আলো পৌছায় না। সেকারণে এসব অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা বিরাজ করে। এমনকি এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও বেশি হতে পারে। এছাড়া চাঁদের বুকে থাকা সবচেয়ে বড় বড় গর্ত এবং গিরিখাত গুলোও এই অঞ্চলে অবস্থিত। এসব একেকটি গর্ত আমাদের পৃথিবীর সাগর উপসাগরের মত বিস্তৃত। এসব কারণেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করা এবং এখানে গবেষণা পরিচালনা করা অনেক কঠিন। এত তীব্র ঠান্ডায় ল্যান্ডার রোভারের যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ নাও করতে পারে।