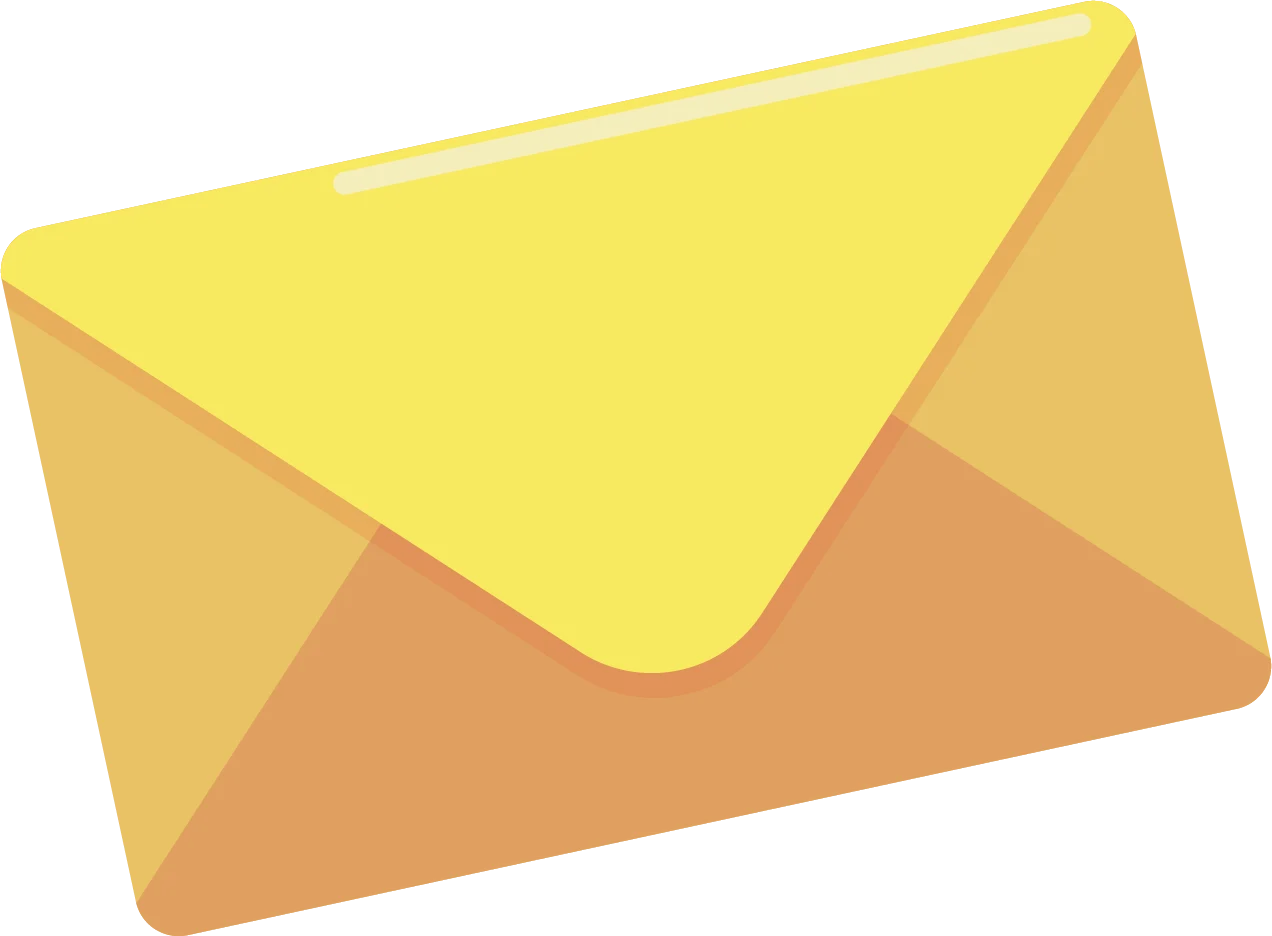ঘড়ি আবিষ্কারের গল্প
ঘড়ি আবিষ্কারের গল্প
ভূমিকা
মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়। কথায় বলে Time is Money. কিন্তু সত্যিকার অর্থে সময় টাকার চেয়েও বহু মূল্যবান। কারন একজন ব্যক্তি যত ধনীই হোক না কেন, টাকা দিয়ে কেউ সময় কিনতে পারে না।
তাই এই অমূল্য সময়ের হিসেব রাখাটা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, বালুঘড়ি সহ বহু ধরনের ঘড়ি আবিষ্কার হয়েছে। আর বর্তমানে আমাদের সবার হাতে থাকা মোবাইল ফোনের কারণে সর্বত্রই ঘড়ির ছড়াছড়ি। অথচ মাত্র চার-পাঁচশ বছর আগেও সময় পরিমাপ করাটা ছিল ভীষণ কঠিন কাজ। এমনকি ইউরোপীয়রা তৎকালীন সময়ের রাজা বাদশাদের শুধুমাত্র ঘড়ি উপহার দিয়ে খুশি করেই, বহু উপনিবেশ দখল করে নিয়েছিল।
প্রাচীন ঘড়ির শুরু
প্রতিদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলের স্ক্রিনে সময় দেখি। কিন্তু ঘড়ি এই পর্যায়ে আসতে কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছে।
ঘড়ির যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে। প্রাচীন মিসরীয়রা তৈরি করেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সানডায়াল ঘড়ি, বাংলায় যাকে বলা যায় সূর্যঘড়ি।
এই সূর্যঘড়ি ছিল একটা চতুষ্কোণ পাথরের উপর তৈরি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে একটি কাঠি বা পিলার দাঁড় করানো থাকত। দিনের বেলা সূর্য উপরে উঠলে এই কাঠির ছায়া প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ত। সেই ছায়া দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে ও দৈর্ঘ্যে দেখা যেত। ছায়ার অবস্থান দেখে মিসরীয়রা বুঝে নিত, এখন সকাল না বিকেল, দুপুর না সন্ধ্যা।
কিন্তু এই সূর্যঘড়ি মেঘলা দিনে এবং রাতের বেলায় কাজ করত না। সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা থেকেই, মানুষ সময় পরিমাপের আরো বিকল্প পদ্ধতি খুঁজতে শুরু করে। প্রাচীন চীনদেশে তৈরি হয় এক অদ্ভুত ঘড়ি, যার নাম incense clock বা ধূপ-ঘড়ি। এটি ছিল ধূপ কাঠির মতো এক ধরনের বস্তু, যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে জ্বলত। এই ধূপ পুড়ে যাওয়ার দৈর্ঘ্য দেখে সময়ের হিসাব রাখা হতো। আবার কোথাও কোথাও এই ধূপে লুকিয়ে রাখা থাকত ছোট ঘণ্টা বা সুতা, যা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে যেত বা শব্দ করত, সেই শব্দেই মানুষ বুঝত যে এক বা দুই ঘণ্টা কেটে গেছে।
গ্রিকদের তৈরী আরেকটি আশ্চর্য ঘড়ি হল Water Clock, যাকে বলা হতো ক্লেপসিড্রা। এটি ছিল দুটি পাত্রের কাঠামো। একটি উপরের দিকে, আরেকটি নিচে। উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে নিচের পাত্রে জমা হতো, আর সেই পানি পড়ার সময় দেখে মিনিট বা ঘণ্টা হিসাব করা হতো। এই একই পদ্ধতিতে জলের বদলে বালু ব্যবহার করেও ঘড়ি তৈরী করা হয়। যা Hourglass বা বালুঘড়ি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এসব ঘড়ির অসুবিধা হল, একবার উপরের পাত্র থেকে নিচের পাত্রে সমস্ত পানি বা বালি পড়ে শেষ হওয়ার সাথে সাথে অাবার ঘড়িটি উল্টে দিতে হত। ঘড়ি উল্টাতে কিছুটা দেরি হলেই সময় গণনায় হেরফের হত। সেকারণেও এই ঘড়িও সম্পূর্ণ কার্যকর ছিল না।
মধ্যযুগে ঘড়ির রূপান্তর
সময়ের হিসেব ছাড়া জীবনটা ছন্দহীন মনে হত। সঠিক সময়ে কৃষিকাজ করা, ধর্মীয় আচার পালন করা, এমনকি রাজকীয় সভা-সমাবেশের সময় নির্ধারণ করার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজই ঠিকমত চলছিল না। তাই প্রাচীন সভ্যতায় সময় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ক্রমাগত আবিষ্কার হতেই থাকে।
১৩শ শতকের দিকে ইউরোপে সময় গণনার ধরণে এক নতুন মোড় নেয়। তখন শুরু হয় যান্ত্রিক ঘড়ির যুগ। এই ঘড়িগুলোতে “ওজন” হিসেবে ভারি পাথর ব্যবহার করা হতো, যা চেইনের মাধ্যমে নিচে নামত এবং ঘড়ির গিয়ার পরিচালনা করত। এই প্রযুক্তিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ছিল escapement mechanism, যা ঘড়ির কাঁটাকে সুনির্দিষ্ট গতিতে সামনে এগিয়ে নিত।
প্রথম দিকের এসব ঘড়ি গির্জার বিশাল বিশাল টাওয়ার গুলোতে বসানো হতো। কারণ সাধারণ মানুষ তখনও ব্যক্তিগত ঘড়ি ব্যবহার করতে পারত না। শুধু ধর্মীয় আচার, প্রার্থনার সময় মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গির্জা টাওয়ারেই বাজতো ঘণ্টা।
১৫শ শতকের শেষের দিকে রেনেসাঁ যুগে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে। তখন সময় গণনাও অনেক এগিয়ে যায়। রেনেসাঁ যুগেই প্রথম পোর্টেবল ঘড়ি বা হাতে বহনযোগ্য ঘড়ির আবিষ্কার হয়। তখন থেকে ধনী ব্যক্তিরা পকেট ঘড়ি ব্যবহার করতে শুরু করেন।
১৬৫৬ সালে ডাচ বিজ্ঞানী Christiaan Huygens তৈরি করেন পেন্ডুলাম ঘড়ি, যেটি ছিল আগের যেকোনো ঘড়ির চেয়ে অনেক বেশি সঠিক। এই ঘড়ির ভুলভ্রান্তির পরিমাণ ছিল দিনে মাত্র ১৫ সেকেন্ড। যা ছিল তখনকার সময়ে এক অভাবনীয় অর্জন।
১৮৮০ এর দশকে যখন ইউরোপে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের মিল না থাকায়, রেল চলালে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই “স্ট্যান্ডার্ড টাইম জোন” বা সময় অঞ্চল নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। তাই তখন থেকে ধীরে ধীরে সময়ের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হয়ে যায়।
এরপর ১৯০৪ সালে স্বয়ংক্রিয় হাতঘড়ি বাজারে আসে। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা সময় দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনে এই ঘড়ির জনপ্রিয়তা বাড়ে। তারপর থেকে সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন প্রযোজনে ঘড়ি ব্যবহার করতে শুরু করে।
অ্যাটমিক ক্লক
সময় মাপার প্রযুক্তি যতই এগিয়েছে, মানুষ ততই আরও নিখুঁত এবং নির্ভুল সময় নির্ণয় করতে চেয়েছে। সেই চাওয়ারই চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৯৬৭ সালে। সে বছর ইতিহাসের সবচেয়ে নিখুঁত ঘড়ি অ্যাটমিক ক্লক বা আবিষ্কার করা হয়। এই পদ্ধতিতে সরাসরি পরমাণুর ভিতরের কণিকাগুলোর কম্পনের ভিত্তিতে সময় গণনা করা হয়। অ্যাটমিক ক্লকে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।
অ্যাটমিক ক্লক এতটাই নিখুঁত যে, এই ঘড়ি এক সেকেন্ডের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ভুল হতে পারে। সহজ করে বললে, এই ঘড়ি যদি কোটি কোটি বছর ধরেও চলতে থাকে, তবুও এর সময়ের হিসাবে এক সেকেন্ডও ভুল হবে না! অতীতে পৃথিবীর সময় পরিমাপের আর কোনো প্রযুক্তি এতটা নির্ভুল হয়নি কখনও।
এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের জীবনে এই ঘড়ি কতটা দরকারী? বাস্তবে, আজকের পুরো ডিজিটাল দুনিয়া এই ঘড়ির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা মোবাইল ফোনে যে সময় দেখি, কিংবা GPS ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাই, এমনকি স্যাটেলাইট যেভাবে সঠিক সময়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে; তার সব কিছুই নির্ভর করে অ্যাটমিক ক্লকের উপর। বড় বড় ইন্টারনেট সার্ভার থেকে শুরু করে বৈশ্বিক ব্যাংকিং সিস্টেম পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ঘড়ির সাহায্যেই প্রতিমুহূর্তে সময় মাপছে।
আর এই নিখুঁত সময় পরিমাপ প্রযুক্তির হাত ধরেই আমরা পেয়েছি স্মার্টওয়াচের মত আরও এক বিস্ময়কর ঘড়ি। এখনকার ঘড়ি শুধু সময় দেখায় না, বরং আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। হাতঘড়ি এখন যেন একেকটি ব্যক্তিগত সহকারী। কারণ স্মার্টওয়াচে দেখা যায় আমরা কতক্ষণ ঘুমালাম, আমাদের হৃদস্পন্দন কত, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কত, আমরা দিনে কত কদম হাঁটলাম কিংবা শরীর থেকে কত ক্যালরি শক্তি খচ হল। এমনকি আমাদের স্ট্রেস লেভেল, শরীরের তাপমাত্রা কিংবা স্বাস্থ্যঝুঁকির পূর্বাভাসও পাওয়া যায় ছোট্ট হাত ঘড়িগুলো থেকে।
অর্থাৎ সময় এখন আর শুধু ঘন্টার হিসেব রাখার বিষয় নয়। বরং সময় গণনা এখন আমাদের বিশ্ব সভ্যতার চলিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। আর অ্যাটমিক ক্লক হল আমাদের সেই শক্তির মূল মেরুদণ্ড।