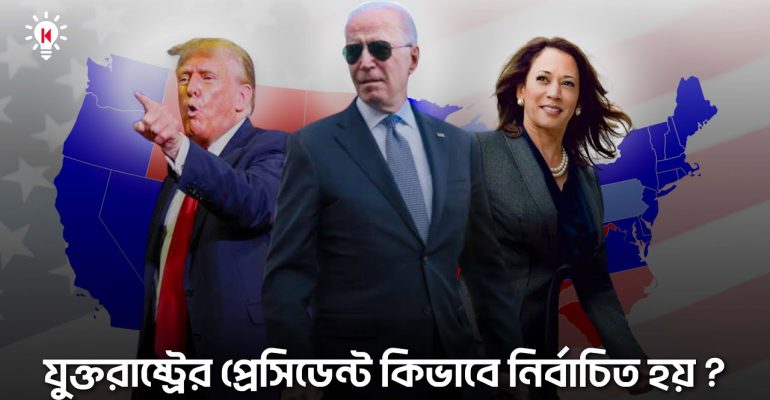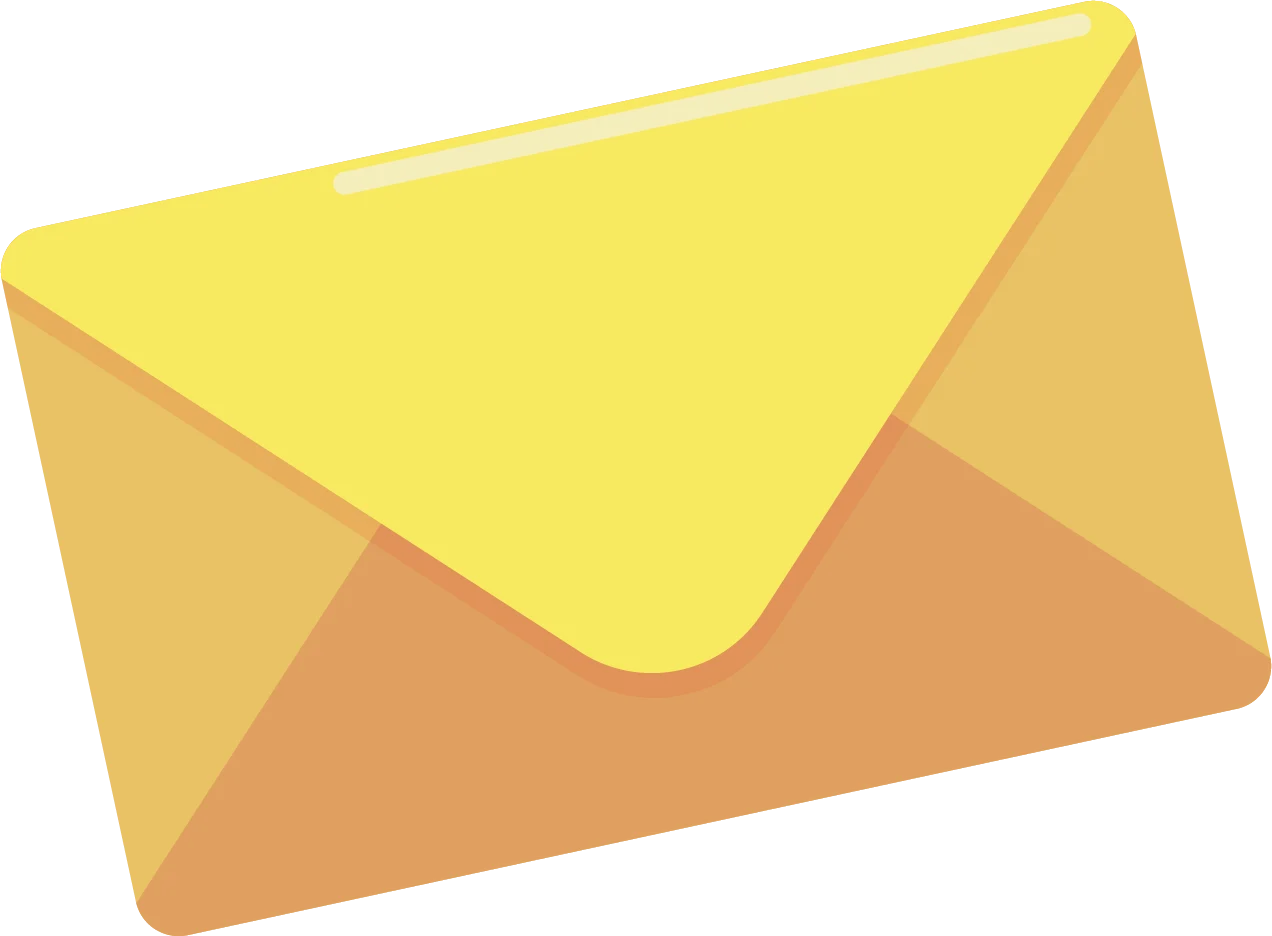আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কিভাবে হয়
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কিভাবে হয়
ভূমিকা
বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এলেই, সারা বিশ্বেই যেন একটি নির্বাচনী আবহ বিরাজ করে। যাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই, তাদেরও অনেকেই এই নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন; শুধু তাই নয় এই নির্বাচন পদ্ধতি এতটাই জটিল যে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু নাগরিকও পরিষ্কার ধারণা রাখে না, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আসলে কিভাবে নির্বাচিত হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় না। ইলেকটোরাল কলেজ নামের একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের পরোক্ষ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এই জটিল পদ্ধতির কারণে, অনেক সময় কোন প্রার্থী জনগণের কাছ থেকে বেশি ভোট পেয়েও, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসতে পারেন না।
যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার আগে, যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা পার্লামেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কে বলা হয় কংগ্রেস। কংগ্রেস মূলত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। কংগ্রেস এর নিম্নকক্ষ কে বলা হয় হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং উচ্চকক্ষ কে বলা হয় সেনেট। নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন এবং উচ্চকক্ষ সেনেট এর সদস্য সদস্য সংখ্যা ১০০ জন। কংগ্রেসের মোট ৫৩৫ জন সদস্যই কংগ্রেসম্যান হিসেবে পরিচিত। তবে উচ্চ কক্ষ সেনেটের সদস্যদের আলাদাভাবে সেনেটর হিসেবে ডাকা হয়। পদাধিকার বলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সেনেটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন।
চার বছর পর পর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে নির্বাচিত করার বিষয়টি প্রধান্য পেলেও, এই নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্যদেরও নির্বাচিত করা হয়। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের মেয়াদ দুই বছর, তাই প্রতি দুই বছর পর পর নিম্নকক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে সেনেটের সদস্যদের মেয়াদ ছয় বছর। তবে সেনেট সদস্যদের নির্বাচন ৩টি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। তাই দুই বছর পর পর সেনেটের তিন ভাগের এক ভাগ আসনে নির্বাচন হয়। আমেরিকার ৫০ টি রাজ্যের প্রতিটিতে ২ জন করে সেনেটর নির্বাচিত হন। সেকারণেই কংগ্রেসে সেনেটরের সংখ্যা ১০০ জন।
ইলেকটোরাল কলেজ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা হলেন, ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যরা। কারণ এরাই মূলত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের বলা হয় ইলেকটর। সহজ করে বলতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে ইলেকটর নির্বাচন করে। এরপর ইলেকটরদের সমন্বয়ে গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।
মূলত কংগ্রেসের সদস্যরাই ইলেকটোরাল কলেজের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ মিলিয়ে কংগ্রেসের মোট সদস্য ৫৩৫ জন। এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি বা ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার নিজস্ব ৩টি ভোট রয়েছে। এই সব মিলিয়ে মোট ৫৩৮ জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে ইলেকটোরাল কলেজ। এই ৫৩৮ জনের কাছ থেকে যে প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ট ভোট পায় সেই হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। কোন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য সর্বনিম্ন ২৭০ টি ইলেকটোরাল ভোট পেতে হয়।
যে রাজ্যের জনসংখ্যা যত বেশি তাদের ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যাও তত বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য হল ক্যালিফোর্নিয়া। তাই এই রাজ্যে সর্বোচ্চ ৫৫টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। তবে ইলেকটোরাল ভোটের সবচেয়ে বিতর্কিত একটি বিষয় হল Winner Take All পদ্ধতি। বিষয়টি সহজভাবে বলতে গেলে, মনে করুন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি পেয়েছে ৩০ টি ভোট এবং রিপাবলিকান পার্টি পেয়েছে ২৫ টি ভোট। এখানে যেহেতু ডেমোক্র্যাটরা বিজয়ী হয়েছে, তাই ধরে নেওয়া হবে যে, শুধু ৩০টি ভোটই নয়, ৫৫টি ভোটই ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে। একেই বলা হয়, Winner Take All বা বিজয়ীরা সব নিয়ে যাবে। উইনার টেক অল পদ্ধতির কারণেই যুক্তরাষ্টের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজের বিষয়টি বেশ বিতর্কিত।
নির্বাচন পদ্ধতি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি যেমন জটিল, তেমনিভাবে এটি বেশ দীর্ঘ মেয়াদী একটি প্রক্রিয়া। তবে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কখন কী ঘটবে, তার দিনক্ষণ সব আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। প্রায় বছর ব্যাপী নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলমান থাকে বলে, যে বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই বছরকে বলা হয় ইলেকশন ইয়ার।
একটি ইলেকশন ইয়ারের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রার্থী বাছাই করার কাজ শুরু করে। এরপর প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, প্রধানতম প্রতিদ্বন্দীরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করার মাধ্যমে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্পন্সরশিপে আয়োজিত এসব প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে।
একটি ইলেকশন ইয়ারে নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরের মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে বলা হয় পপুলার ভোট। পপুলার ভোটে যে প্রার্থী বেশি ভোট পায় সেই ব্যক্তিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় না। পপুলার ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেসের যে সদস্যরা নির্বাচিত হন, তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকটোরাল কলেজ। এই ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে যে প্রার্থী জয়ী হয়, তিনিই পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেব ক্ষমতা গ্রহণ করেন।
সাধারণত ইলেকশন ডে বা নির্বাচনের পরের দিনই বোঝা যায় যে, কে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে। তবে এই পপুলার ভোটের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হয় আরো বেশ কয়েক দিন পরে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ডাকযোগে ভোট দিয়ে থাকে। সেসব ভোট গণনা করতে বেশ সময় লাগে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ২৩ শতাংশ ভোটার ডাকযোগে ভোট দিয়েছিল। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে ভোট বাই মেইল বা মেইল ইন ভোটের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ইউএস ইলেকশন অ্যাসিসটেন্স কমিশনের তথ্য মতে, ২০২০ সালে প্রায় ৪৬ শতাংশ ভোটার ডাকযোগে ভোট দিয়েছে। এসব ভোট গণনা ছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণে পপুলার ভোটের ফলাফল প্রকাশ করতে ইচ্ছাকৃতভাবেই বেশ কয়েকদিন সময় নেওয়া হয়। এর বাইরে কোন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী যদি নির্বচনে কারচুপির অভিযোগ আনে, সেক্ষেত্রে সেসব অভিযোগ তদন্ত করে তারপর নভেম্বর মাসের মধেই পপুলার ভোটের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়। তবে এটিই চূড়ান্ত ফলাফল নয়।
ইলেকশন ইয়ারের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় বুধবারের পরের মঙ্গলবার ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যরা নিজ নিজ রাজ্যের রাজধানীতে ইলেকটোরাল ভোট প্রদান করেন। এই ভোটের মাধমেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। অতীতে যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেত, তিনিই ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য আলাদা ব্যালট সৃষ্টি করা হয়।
ডিসেম্বরের চতুর্থ বুধবারের আগে ইলেকটোরাল কলেজের ভোট গুলো সিনেট প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্কাইভিস্টের কাছে পাঠাতে হয়। জানুয়ারির ৩ তারিখে নব নির্বাচিত সদস্যরা কংগ্রেসে সমবেত হন। এবং জানুয়ারির ৬ তারিখে কংগ্রেসের সম্মেলনে ইলেকটোরাল ভোট গণনা করা হয়। ভোট গণনা শেষে সেনেটের প্রেসিডেন্ট, পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করেন।
এরপর নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে তার মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য কিছুদিন সময় দেওয়া হয়। সবশেষে জানুয়ারির ২০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত, দেশটির পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বিতর্কিত দিক
যুক্তরাষ্টের নির্বাচনে সাধারণ জনগণের ভোটের চেয়ে ইলেকটোরাল কলেজের ক্ষমতা বেশি। সেকারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা মূলত এই ইলেকটোরাল ভোট জেতার জন্যই লড়াই করেন। জটিল ইলেকটোরিয়াল ভোটের ভালো এবং খারাপ, দুটি দিকই আছে। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, েকান প্রার্থী পপুলার ভোটে এগিয়ে থাকলেও, তিনি ইলেকটোরাল ভোটে হেরে যেতে পারেন। তারমানে কোন ব্যক্তি আমেরিকার জনগণের ভোটে হেরে গেলেও, ইলেকটোরিয়াল কলেজের ভোটে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন।
এখনও পর্যন্ত মোট ৫ বার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বিগত ৫টি নির্বাচনের মধ্যেই দুই বার এ ধরনের নজির রয়েছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারী ক্লিনটন পপুলার ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে ৩০ লক্ষ বেশি ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে Winner Take All পদ্ধতির কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকটোরাল ভোটে বিজয়ী হন। তার আগে ২০০০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ ডাব্লিউ বুশ ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাল গোরের চেয়ে সাড়ে ৫ লাখ ভোট কম পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ইলেকটোরাল কলেজে বেশি ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকে চলে আসা এই ইলেকটোরাল কলেজ নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও, তারা এই পদ্ধতি বাদ দিতে চায় না। কারণ নির্বাচনের সময় দেশটির বড় বড় রাজ্যগুলো যেন ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে উপেক্ষা করতে না পারে; সেজন্যই ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে ছোট রাজ্যগুলোকেও বড় রাজের সমান অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যই হয় ডেমোক্র্যাটদের না হয় রিপাবলিকানদের দখলে। তাই এসব রাজ্যের ভোটের ফলাফল কি হতে পারে তা অনেকটা আগে থেকেই আঁচ করা যায়। সেকারণে এ সমস্ত রাজ্যের ভোটাররা ভোট দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী থাকে না। তবে কিছু রাজ্য আছে যেখানে কখনও ডেমোক্র্যাট আবার কখনও রিপাবলিকানরা বিজয়ী হয়। তাই এদের উপরই আসলে নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে। সেকারণে এসব রাজ্যকে বলা হয় ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেট। অর্থাৎ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আসল লড়াই এই রাজ্যগুলোতেই হয়।